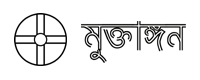কবি শামসুর রাহমানের একটি বিখ্যাত কবিতা আছে, নাম ‘সফেদ পাঞ্জাবী’। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর উপর লেখা কবিতাটি। কবিতাটিতে শামসুর রাহমান অবিসংবাদিত এই জননেতার মনুমেন্টাল চরিত্রটি তুলে ধরেছেন। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে একজন অসাম্প্রদায়িক মাওলানার মানবপ্রেমের গাথা কবি এখানে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। বাম চেতনার প্রতিভূ এই কমিউনিস্ট মাওলানা সারাজীবন অসাম্প্রদায়িক শোষণহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন এবং এই আদর্শে লক্ষ কোটি বাঙালিকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। তবে এ বছরের ৬ এপ্রিল ঢাকায় লক্ষাধিক সফেদ পাঞ্জাবিওয়ালার যে-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো, তা কবি শামসুর রাহমানের ‘সফেদ পাঞ্জাবী’ কবিতার মূল সুরকে ছিন্নভিন্ন করে এবং ভাসানীর অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভূলুন্ঠিত করে যেন একটি সফেদ সন্ত্রাসের রুপ পরিগ্রহ করেছিল। সমস্ত বাংলাদেশ শুধু তাকিয়ে দেখলো আর ভাবলো, আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম? অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো আমাদের চেনাজানা ভূবনের বাইরে থেকে পঙ্গপালের মতো একদল লোক আমাদেরকে তাদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে আবার তাদের ডেরায় ফিরে গেল। হেফাজতে ইসলাম নামে একটি সংগঠন ছিল আয়োজক এই সফেদ সন্ত্রাসের। তারা ‘ইসলাম গেল’ ধুয়া তুলে মুক্তচিন্তার আদর্শে বিশ্বাসী ব্লগারদের ফাঁসি চাইলো, নারীদের অবরোধবাসিনী করা সহ নানা অবমাননাকর বক্তব্য দিলো এবং সেই সাথে একজন নারী সাংবাদিককে বেধড়ক পেটালো। নারীর বিরুদ্ধে তারা কত কী যে করতে পারে তার একটা নমুনা প্রদর্শন করে গেলো। আর সবশেষে জাতিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ১৩ দফা দাবি উপস্থাপন করে গেলো — যা এই বাংলাদেশকে মধ্যযুগীয় তালেবানি রাষ্ট্র বানানোর ঘৃণিত বাসনার প্রতিফলন। এই ১৩ দফা দাবির মধ্য দিয়ে নারীদের অপমান করা হয়েছে, মুক্তচিন্তাকারী মানুষদের অপমান করা হয়েছে, শিল্পীদের অপমান করা হয়েছে, অন্যধর্মের সংস্কৃতিকে অপমান করা হয়েছে এবং সর্বো্পরি প্রকৃ্ত ইসলামের চেতনাকেও ধুলায় লুণ্ঠিত করা করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের এই মধ্যযুগীয় চিন্তাচেতনা বাস্তবায়নের নীল নকশার খসড়া। আমার জানামতে অনেক বিবেকবান মানুষই তাদের আস্ফালন আর টিভির পর্দায় দেখতে চায়নি, ঘৃণাভরে টিভির সুইচ অফ করে দিয়েছে। বিশেষ করে নারী সমাজ ফুঁসে উঠেছে তাদের এই সফেদ সন্ত্রাসে। তবে আশার কথা এই হুঙ্কারে কেউ গুটিয়ে যায়নি। বরং তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। যেদিন শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে হেফাজতের সন্ত্রাসীরা আক্রমণের পায়তারা করছিলো সেদিন আমি দেখেছি মধ্যবয়সী নারীদেরকেও লাঠি হাতে তুলে নিতে। নারীরা সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে…
এ বছরের ৬ এপ্রিল ঢাকায় লক্ষাধিক সফেদ পাঞ্জাবিওয়ালার যে-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো, তা কবি শামসুর রাহমানের ‘সফেদ পাঞ্জাবী’ কবিতার মূল সুরকে ছিন্নভিন্ন করে এবং ভাসানীর অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভূলুন্ঠিত করে যেন একটি সফেদ সন্ত্রাসের রুপ পরিগ্রহ করেছিল। সমস্ত বাংলাদেশ শুধু তাকিয়ে দেখলো আর ভাবলো, আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম? [...]