[বইয়ের দেশ (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯) থেকে সংকলিত]
সকলেই একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছে
আমাদের এই সময়টাকে সবদিক দিয়ে সর্বার্থে জড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁরই কথায়, ‘শিকড় দিয়ে আঁকড়ে’ আছেন। তাই কবি শঙ্খ ঘোষ-এর কোনও বিশেষ পরিচয় হয় না। তাঁর অস্তিত্বই তাঁর পরিচয়। বাংল কবিতায় প্রায় ষাট বছর ধরে তিনি তৈরি করে নিয়েছেন এমন এক পথ, যে-পথে স্বল্প যাত্রী, যে-পথে সামান্য আলো জ্বলে। সমালোচনায় নিয়ে এসেছেন সর্বজনবোধ্য এক জ্ঞানচর্চার দিশা, সংক্রামকভাবে বারবার সাড়া দিয়েছেন সংকট সময়ে। এই কবির সঙ্গে কথা বলেছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়। লেখার কথা, জীবনের কথা, ঘরের আর বাইরের কথা।
. . .
সুমন্ত : বেশির ভাগ কবি বা লেখকেরই তো লেখা শুরুর সময়ে আটপ্রহরের লেখকবন্ধুরা এসে যায়, একসঙ্গে তারা লেখে, তর্ক করে, লেখা ছাপতে দেয়, তারপর একদিন যে যার পথে চলতে থাকে। আপনার ক্ষেত্রেও কি তেমন হয়েছিল?
শঙ্খ : তেমন কোনো লেখকবন্ধুর দল? না, শুরু করবার দিনগুলিতে একেবারেই হয়নি সেটা। এ-ব্যাপারে একটু লুকিয়ে-থাকা স্বভাবই ছিল আমার। ভরসা করে কাউকে দেখাব লেখা, আবার তা নিয়ে তর্কও করব, এতটা উদ্যম ছিল না, সাহসও ছিল না।
প্র : তাহলে, একেবারে শুরুতে কাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেতেন? কাউকে-না-কাউকে তো দেখিয়েছেন?
উ : স্কুলজীবনে বা কলেজজীবনের একেবারে গোড়ায় খুব ঘনিষ্ঠ দু’-একজন বন্ধু – নিজেরা যারা লিখত না – তেমন কাউকে পড়িয়েছি কখনও। তারা যে কেবল উৎসাহ দিত তা নয়, তারও চেয়ে বেশি, বাড়তি একটু বাহবাই দিত। এমনকী ছাপাবার জন্যও পীড়াপীড়ি করত।
প্র : গোড়ার দিকে তিনটে কবিতার খাতা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন কেন তবে? এইরকম একটা কথা পড়েছি কোথাও।
উ : হ্যাঁ, বলেছি কিছুদিন আগে। হস্টেলের এক বন্ধুর সঙ্গে একটু মান-অভিমানের ঘটনা ছিল সেটা। ও পড়েছিল কবিতা, কিন্তু সেটা আবার রটিয়েও দিয়েছিল। সবাইকে ও জানিয়ে দিল কেন? এই অভিমান থেকে কাণ্ডটা। ছেলেমানুষিই হয়েছিল। অবশ্য ছেলেমানুষই তো ছিলাম তখন। ষোলো বছর বয়সের ঘটনা ওটা।
প্র : কোন হস্টেল? রামকৃষ্ণ মিশনের?
উ : রামকৃষ্ণ মিশনের। এখন বেলঘরিয়াতে প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে যে রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম, খুবই ছোট চেহারায় সেটা তখন – মানে দেশভাগের সময়টায় – ছিল মানিকতলার হরিনাথ দে রোডে। সেখানে কাটিয়েছি দু’বছর। বেশ নতুন রকমের অভিজ্ঞতা ছিল সেটা।
প্র : তবে তো একটা নীতিনিয়মে বড় হয়েছেন বলে মনে হয়। আপনাদের পারিবারিক অনুশাসনও কি খুব কঠোর ছিল? যত্র তত্র যখন তখন যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারতেন?
উ : মিশনে একটা নীতিনিয়ম তো ছিল ঠিকই। তার কতটা মেনে চলতাম সে আলাদা কথা। কিন্তু আমাদের পারিবারিক অনুশাসন তেমন কিছু কড়া ছিল না। যখন তখন যার তার সঙ্গে যত্র তত্র ঘুরে বেড়াবার পথে প্রত্যক্ষ তেমন বাধা ছিল না। পিছিয়ে-পড়া ছেলেরা – বা যাদের সঙ্গে মিশলে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায় বলে ভাবা হত – আমার চলাফেরার বেশির ভাগটাই ছিল তাদের সঙ্গে। বাবার কাছে কেউ কেউ এ নিয়ে নালিশও করেছেন, তবে বাবা তাতে কান দিতেন না বড়-একটা। সন্ধের অনেক পরে বাড়ি ফিরে দু’-একবার তর্জন শুনিনি তা নয়। সেটা মায়ের কাছে। একবারই শুধু বড় মাপের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন বাবা, শেষ পর্যন্ত সেটা করে উঠতে পারেননি।
প্র : তাহলে কীভাবে ছড়িয়ে পড়ত শৃঙ্খলার ব্যাপারটা মনে? কোথায় বাধা ছিল? কোথায়ই বা মুক্তি?
উ : এখন ভেবে দেখতে গেলে বুঝি মুক্তিটাই ছিল বেশি। আর শৃঙ্খলা? সে তো ছিলই না তেমন। গোড়ার দিকে তার কোনও দরকারও হয়নি। বাবা ছিলেন হেডমাস্টার, আর আমাদের বাসাবাড়ি থেকে স্কুলঘরে পৌঁছতে সময় লাগত বড়জোর দু’মিনিট। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ক্লাস সিক্সের আগে আমায় স্কুলে পাঠাননি বাবা। পাড়ার বন্ধুরা দশটার মধ্যে চলে যায় স্কুলে, বিকেলের আগে আর পাওয়া যাবে না তাদের। আমার সময়টা ফাঁকা, যা-খুশি করে বেড়াবার বা ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা। সেটা ভালও লাগে। আবার খারাপও। বাড়িতেও নিয়মবাঁধা পড়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। শেষে একদিন মায়ের কাছে অনেক দরবার করে ভর্তি হবার ছাড়পত্র পাই। বাবা নাকি রাগই করেছিলেন এতে। এ-রহস্যটা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু ওই-যে দশ বছরের আগে পর্যন্ত শৃঙ্খলাহীনভাবে দিন কাটানো, তার জেরটা আর কাটাতে পারিনি।
প্র : ‘করুণ রঙিন পথ’ লেখাটা পড়ে মনে হয় আপনার নানা আবদারের আশ্রয় ছিলেন আপনার মা। একটা বড় পরিবারের মধ্যে ওঁকে কেমনভাবে পেয়েছেন?
উ : ঠিকই, স্কুলজীবন শুধু নয়, কলেজজীবনেও অনেক অন্যায় আবদার করেছি মায়ের কাছে। অল্প আয়ের বড় পরিবার, থেকে-থেকেই মা বলতেন রাবণের সংসার। আর সেসব দিনে স্কুলপ্রধানের মাইনে ছিল বড়জোর একশো টাকা। সংসার সামলাতে মাকে কেমন হিমশিম খেতে হত, সে তো দেখেছি। তা সত্ত্বেও তুচ্ছ কারণে একটা আধুলি বা একটা টাকার জন্য ঘুরঘুর করেছি পিছনে, জানতামই যে কিছুক্ষণ পরে আঁচলের খুঁট থেকে বের করে দেবেন কিছু। ভাইবোনদের মধ্যে এ-অন্যায়টা বোধহয় আমিই করতাম কেবল। মা সকাল থেকে হেঁসেল নিয়ে পড়ে আছেন, সবাইকে ডেকে ডেকে খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু তারই সঙ্গে দুপুরে বিশ্রামের সময়ে শুয়ে শুয়ে কোনও একটা বই পড়ছেন, বিকেলে কখনও-বা কারও সঙ্গে এখানে-ওখানে বেরিয়ে পড়ছেন নিছক বেড়াবার জন্য কিংবা কোনও সভা শুনতে। অন্য দিকে, বাবা সারাদিনই – রাতেও – ব্যস্ত থাকেন ইস্কুলের কাজে, কোনওই খবর রাখেন না সংসারের। আর এই না-রাখাটাই যে ঠিক কাজ, এ-রকমই একটা বিশ্বাস যেন মায়ের। ওই যে স্কুল বা লেখাপড়া নিয়ে বাবার সময় কেটে যায় তাতে একটা তৃপ্তিরই বোধ ছিল তাঁর। মুখে যদিও কখনও কখনও বলতেন ‘খবর রাখে না সংসারের কিছুই’, কিন্তু লক্ষ করতাম এ গঞ্জনাবাক্যে মায়ের মুখে একটা গর্বভাবই ফুটে উঠত, যেমন গর্ব নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের বলতেন অনেকসময়, ‘আমার পোলারা এক গ্লাস গড়াইয়াও খাইতে পারে না।’ শুনে শুনে আমরাও ভাবতাম ওটা যেন খুব গুণেরই কথা।
প্র : বাণারিপাড়া, পাকশি আর সুপুরিবনের সারি ঘেরা মামাবাড়ি – আপনার লেখায় এই পরিসরটাই বারবার ফিরে আসে দেশ হয়ে। কলকাতা আর ভারতবর্ষ যেখানে প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত। ওই দেশ যদি আশ্রয় দেয়, এই দেশ ছুড়ে ফেলতে চায়। এই বিপরীতের টানে কোথায় আপনার দেশ – চোখ বেঁধে দিলে পা যেখানে একটা চেনা স্পর্শ খুঁজে নেয়?
উ : তোমার এই প্রশ্নটার গোড়ায় সাহিত্য পড়ার একটা মৌলিক সমস্যা লুকনো আছে। সমস্যটা হল, আত্মজৈবনিক ভিত্তি আছে বলে বোঝা যায় যেসব গল্প-উপন্যাসের, তার কতটুকু বা কোনটুকুকে লেখকের আত্মজীবন বলে বুঝব। ‘শ্রীকান্ত’ বা ‘ত্রিদিবা’ বা ‘আত্মপ্রকাশ’ থেকে যে-কোনো ঘটনা বা সংলাপ বা লাইন তুলে নিয়ে কি বলতে পারি, যে ওটা শরৎচন্দ্রের বা গোপাল হালদারের বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনকথা? ওইখানে একটা জটিলতা তৈরি হয়ে যায়। সুপুরিবনের সারি-ঘেরা বাড়িটি কিন্তু ও-বইয়ের কিশোর নায়কের মামাবাড়ি, আমার নয়। আমার মামাবাড়ি চাঁদপুরে, ঢাকার কাছে। আর সুপুরিবনটা কাকা-ঠাকুর্দার বাড়ি। আমার লেখায় চাঁদপুর বড় একটা আসে না। আর, ঠিকই, বাকি দুটো জায়গা ফিরে ফিরেই আসে। তারও মধ্যে পাকশি বিষয়ে টানটা একটু বেশি, কেননা সাত থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত পদ্মাপারের – একেবারে আক্ষরিক ভাবেই পদ্মাপারের – ছোট ওই মফস্সলে সময় কেটেছে আমার। সেইখানেই আমার পড়াশোনা। পিছনে বন, সামনে নদী, ডাইনে-বাঁয়ে খেত-ছড়ানো গ্রাম, এরই মধ্য দিয়ে বড় হবার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। আর ওই বয়সটা তো সবারই পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণের, সবচেয়ে সঞ্চয়ের, সবচেয়ে সংলগ্নতার সময়। পাকশিকে তাই ভুলতে পারি না।
আশ্রয় দেওয়া আর ছুড়ে ফেলতে চাওয়া কথা দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা সরলীকরণ আছে। এটা ঠিক যে, দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন যাঁরা, প্রথম দিকটায় তাঁদের শারীরিক-মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে অনেক। অস্তিত্বই বিপন্ন হয়েছে, শুনতে হয়েছে নানা রকমের কটু কথা, প্রথম দিকটায় তার ধকল কাটিয়ে ওঠা শক্তই হয় অনেকের পক্ষে। কিন্তু সেইটেই তো একমাত্র ছবি নয়। এদিককার আরও অসংখ্য মানুষের সেবা বা ত্যাগও ওর সঙ্গে জড়ানো না থাকলে, আশ্রয়েরও দ্যোতনা না থাকলে, এত বড় একটা দুর্ভার কি সামলানো যেত? আশ্রয়-নিরাশ্রয়ের যে-কথাটা তুলেছ, সেটা আসলে একটা দার্শনিক সমস্যা। অতীতকে ছুঁয়ে বর্তমানকে বুঝবার কথা, ‘আমি’ হয়ে উঠবার সমস্যা। এসব বাস্তব অভিজ্ঞতায় সে-সমস্যার শেকড় অবশ্য থেকে যায়, আর লেখায় হয়তো সেটা পৌঁছয় অনেকটা প্রতীকের মতো।
প্র : মেয়েরা আপনার লেখায় বলে ‘আমরা আজও কক্ষনও নই আমি।’ কেন? আপনার দিদি-বোনদের কেমনভাবে পেয়েছেন?
উ : খুবই নিবিড়ভাবে। পুজোর সময় দেশের বাড়িতে – বাণারিপাড়ায় – কিংবা অন্য জায়গাতেও অনেকসময়, খুড়তুতো-পিসতুতো ভাইবোনেরা হুল্লোড় করতাম একসঙ্গে। একুশ-বাইশজন মিলে যেতাম তখন, তবে তার মধ্যে ভাইয়ের সংখ্যা ছিল বড়ই কম। ওই জমায়েতের বেশির ভাগটাই ছিল বোনেরা, দিদিরা। খেলাধুলো, আবদার, তর্জন সবটাই চলত ওদের সঙ্গে। কিন্তু একটা জিনিস অবাক করত, ভাইরা যত স্বাধীন, ওরা যেন ততটা নয়। এমনকী লেখাপড়ার ব্যাপারেও একটা ভেদ ছিল। স্বাধীনতার আগে অল্পই তারা পেয়েছে স্কুল-কলেজে পড়বার সুযোগ। আর তারপর তো একটু একটু করে চারপাশে দেখতে পেলাম নানা রকমে তাদের আটকে থাকা চেহারা। এ-সমাজে যেন নিজের মতো হয়ে ওঠার কোনও অধিকার নেই ওদের।
প্র : ‘যমুনাবতী’ থেকে শুরু করে সেদিন লেখা ‘ছোট্ট একটি কিশোরী বলছিল’ পর্যন্ত আপনার কবিতায় নানা বয়সের আর নানা ঘরের মেয়েরা তাদের কথা বলে যায়। কখনও তাদের স্বরটাই কবিতার একমাত্র স্বর হয়ে আসে। কবির সঙ্গে কোনও ভেদ থাকে না। ছোটবেলা থেকেই কি এই মনটা তৈরি হচ্ছিল? এর কি কোনও ইতিহাস আছে?
উ : অভিজ্ঞতাই একটা ইতিহাস, এ-ছাড়া ইতিহাস কিছু নেই। অবশ্য যদি-না বলা যায় যে বোনদের ওইভাবে দেখাটাও একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। এক-একটা সময়ে এক-একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার ধাক্কা থেকে উঠে এসেছে কবিতাগুলি। তবে, নানা বয়সের বা নানা স্তরের মেয়েরা যে আমার কবিতায় অনেকসময়ই তাদের স্বর রেখে গেছে, বছর পনেরো আগে পর্যন্ত সেটাকে তেমন সচেতনভাবে লক্ষও করিনি আমি। আজকালকার নারীবাদী ভাবনাচিন্তার প্রসারের ফলে নতুন যেসব সমালোচনা, তার থেকেই এটা নজরে এসেছে আমার। লক্ষ করে একটু অবাকই হয়েছি।
প্র : তুলনায় আপনাদের সমসাময়িকেরা, কৃত্তিবাসের কবি বা গদ্যলেখকরা বিশেষভাবে পুরুষের দৃষ্টি আর মন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেটাই তাঁদের জোরের জায়গা। এঁদের লেখা আপনার কাছে কোনও প্রশ্ন তুলত না?
উ : না। কেননা, ওই যে বললাম, গোড়ার দিকে ওইভাবে পড়তামই না কবিতা। কবিতার মধ্যে সংকটাপন্ন মেয়েরা আছে কী নেই, সচেতনভাবে লক্ষই করতাম না সেটা। ছেলেরা ছেলেদের মতো লিখবে, তাদেরই অভ্যাসগত দৃষ্টিতে, এ যেন ধরে নেওয়াই ছিল। মেয়েদের কথা বলবে মেয়েরা, এইরকমই যেন নিয়ম। তবে, সেই মেয়েদেরও কথা একেবারে আত্মস্বাতন্ত্র্য নিয়ে বলা, ক্ষমতাবৃত্ত ক্ষমতাপেষণের দিক থেকে লক্ষ করা তাকে, আর্তনাদ আর প্রতিবাদ, সেটা বেশ প্রকট হয়ে উঠত আমাদের বন্ধু কবিতা সিংহের লেখায়। বলা যায়, কবিতাই যেন একটু একটু করে চেতনা এনে দিচ্ছিল আমাদের মনে। ওর লেখার মধ্যে তো ছিলই, আশির দশকে ও নব্বইতে ওর ব্যক্তিগত দু’-একটা চিঠিতেও টের পেতাম পুরুষবন্ধুদের কাছে ওর নানা রকম আঘাত পাবার কথা, উপেক্ষা-অবহেলার কথা। আমার মনে অন্যদের কবিতা বিষয়ে যে-প্রশ্ন ছিল না, দীর্ঘকাল জুড়ে কবিতা সিংহের মনে নিশ্চয়ই ছিল সেটা। পরে, নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার স্বভাবতই তার নামটা জুড়ে গেছে।
প্র : কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কোনও-একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ তৈরি হলে – অর্থাৎ নারীবাদী, দলিত, কৃষ্ণকায়, কমিউনিস্ট – যে-কোনও পজিশনে অনড় হয়ে দাঁড়ালে কি কবিতার ক্ষতি হয় না? তাহলে কীভাবে মারি ইভান্স, অরুণ কোলাৎকার অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায় এত অসামান্য লেখা লেখেন? এঁরা তো আপানারও প্রিয় কবি?
উ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া অন্য দু’জনও যে আমার প্রিয় কবি তা জানলে কেমন করে? বলিনি তো কোথাও। অবশ্য মিথ্যে ভেবেছ তা বলছি না। বরং বিস্ময়ের কথা যে এই কয়েকমাস ধরে কোলাৎকারের The Boatride and Other Poems নামের মৃত্যূত্তর সংকলনটা থাকছে আমার সঙ্গে সঙ্গে। মারি ইভান্সও আমার পছন্দের। কিন্তু, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা কোলাৎকার কি তোমার কলা ওই তকমাগুলির কোনও একটাতে আটকে ছিলেন? ‘পদাতিক’ থেকে ‘চিরকুট’ পর্যন্ত কেউ-বা বলতেও পারতেন যে এ হল কমিউনিস্ট কবিতা। এমনকী, ধরা যাক, ‘ফুল ফুটুক’ও। কিন্তু তারপর থেকে কি ওরকম কোনও ‘নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ’ মনে রেখে পড়া যায় ওঁর কবিতা? যায় না বলেই, দেখা-সেই ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যখন সোমনাথ লাহিড়ীর মতো একজন সর্বার্থে শ্রদ্ধেয় মানুষ সুভাষদার সদ্য-প্রকাশিত একটা কবিতা পড়ে ‘পরিচয়’ পত্রিকা ছুড়ে ফেলেছিলেন দূরে, কিংবা তাঁর একান্ত বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মধ্যষাটে একবার আক্ষেপ করেছিলেন, ‘এসব আজকাল কী লিখছে সুভাষ’! তকমায় যে আটকে থাকেননি উনি, এইটেই ওঁর জোর। কিংবা কোলাৎকার। নিজে যিনি বলেছিলেন, ‘যা কিছু আমার ঐতিহ্য তার সবটুকুতেই আমার দাবি’, তাঁর একটা কোটরে পুরবে কী করে? সব কিছুর ইতিহাস তাঁর চাই, ধর্ম থেকে রুটি-বানানো পর্যন্ত সব। নামদেব তুকারাম থেকে অনুবাদও করবেন তিনি, এ-ও বলবেন যে এ-দেশের সবচেয়ে ভাল কবিতাগুলির অনেকটাই লেখা হয়েছে এলিয়েনেশনের বোধ থেকে, ভক্তি কবিতারাও মধ্যে আছে সেটা, আছে দলিত কবিতারও মধ্যে, লোকগীতির মধ্যেও। কিংবা ধরো, যে কবিতা সিংহের সূত্র ধরে কথাটা উঠল, নারীবাদী বিশ্লেষণ দিয়ে ঘিরে ফেলা যায় কবিতার সমস্ত লেখা? মনে হয় না। দৃষ্টিকোণগত এক-একটা অভিধা দিয়ে আলোচকেরা বেঁধে ফেলতে চান কবিকে তাঁদের সুবিধের জন্য। কোনও সত্যিকারের কবি সেটাকে গ্রাহ্য করতে পারেন না। ভাল কবিতা সব সময়েই মুক্ত।
প্র : সাহিত্য পড়তে পড়তে ভাল লেখা বা খারাপ লেখা নিয়ে মনে কি কোনও মীমাংসা তৈরি হয়?
উ : ভাল-খারাপ তো লাগেই, তবে তার থেকে ভালত্ব বিষয়ে যে কোনও তাত্ত্বিক মীমাংসাসূত্র তৈরি হয়ে ওঠে, তত দূর বলতে পারি না। মানে, আমার কথা বলছি। এই পর্যন্ত কখনও মনে হয় ভাল লেখার মধ্যে লেখকের মানসিক একটা স্বচ্ছতা থাকে। আর থাকে কোনও একটা বিশ্বব্যাপ্ত বোধের ইশারা। জীবনটাকে, গোটা জগৎটাকে নতুন-একটা চোখে দেখতে পাবার ক্ষমতা, সে-জীবন বা সে-জগৎ বিষয়ে কোনও-যে সিদ্ধান্ত মেলে তা হয়তো নয়, একটা প্রশ্ন জাগিয়ে তোলাই বড় কথা। সেই প্রশ্ন দিয়ে আমাকে আলোড়িত করে তোলা, একটা অভিমুখীনতা তৈরি করা, এইটেই আসল। তার মধ্যে অনেক ওঠাপড়া থাকে, অনেক কাটাছেঁড়া থাকে, সব সময়ে মসৃণতা না-ও থাকতে পারে। মসৃণতা আর স্বচ্ছতা কিন্তু এক কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জীবনানন্দকে একবার লিখেছিলেন যে উঁচু জাতের লেখার মধ্যে একটা শান্তি একটা serenity থাকে। জীবনানন্দ প্রতিবাদ করেছিলেন সে-কথার। এ-ব্যাপারে আমি জীবনানন্দের কথাই মানি। সাহিত্যের ভিতরকার একটা বিক্ষোভ বা অশান্তির তুমুল তাড়নার কথা বলেছিলেন তিনি সঙ্গতভাবেই।
প্র : নিজের লেখার সময়ে এই আদর্শগুলো আপনার মনে আসে?
উ : না না, একেবারেই না। কোনও কিছুকেই আদর্শ ভেবে নিয়ে আমি লিখতে পারি না। আর তা ছাড়া, এসব উঁচু জাতের সাহিত্যের কথা যখন চলছে তখন আমার লেখার প্রসঙ্গ তুললে একটু মানবিভ্রমের অপরাধ ঘটে যাবে। মনে আছে তো, শব্দটা একবার ব্যবহার করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়? একটু আগে যে-কথাটা হচ্ছিল, সে বিষয়ে উনিও বলেছিলেন যে মানুষ নিয়েই সাহিত্য, মতামতের গোঁড়ামিতে মানুষ ছোট হয়ে যায়। আর অন্য দিকে, আমাদের জাতীয় মানবিভ্রমের থেকে বাঁচবার উপায় বলেছিলেন, একটু আত্মবিশ্লেষণ আর একটু পেসিমিজম। ‘আমরা ও তাঁহারা’ বইটার মধ্যে আছে এসব।
প্র : আত্মবিশ্লেষণ বা আত্মসমালোচনা কত দূর গেলে আত্মপীড়ন হয়ে ওঠে?
উ : এটা হিসেব করে বলা শক্ত। তবে, একটু হালকা করে বলতে ইচ্ছে করে, আত্মসমালোচনায় মন যখন বেশ খুশি খুশি লাগে তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে ওটা আত্মপীড়ন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মর্ষকামিতার মধ্যে একটা আনন্দ আছে না, তৃপ্তিবোধ? আত্মপীড়ন করে দেয় নিষ্ক্রিয়। আর আত্মসমালোচনা – সত্যিকারের আত্মসমালোচনাই যদি হয় – তাতে তৈরি হয় খানিটা মানসিক উত্তরণ বা নবোদ্যমের সম্ভাবনা।
প্র : ‘বটপাকুড়ের ফেনা’র টুকরো লেখাগুলোয় বারবারই আপনি অজানা অনামী সব হিতকরী উদ্যোগের কথা বলেছেন, যেখানে বর্তমান সময়টারও একটা আশা করবার মতো চরিত্র তৈরি হয়। একই সঙ্গে, ‘এখন সব অলীক’ বা ‘অবিশ্বাসের বাস্তব’-এর মতো বইপত্রে সমসময় নিয়ে একটা হতাশাবোধ টের পাই। সময়কে আপনি কীভাবে বুঝতে চান তাহলে? তার কি চরিত্র আছে কোনও?
উ : সম্ভবত জানতে চাইছ চলতি সময়টাকে আমি হতাশাজনক ভাবি, না কি সেখানে আশা-আশ্বাসেরও কোনও জায়গা আছে। প্রথমে বলি, জীবনে আশা-নিরাশার এই দ্বিকোটিক বিভাজনটায় আমার তেমন সায় নেই। অনেকসময়, ওসব জড়িয়ে থাকে একই সঙ্গে একই মনে। যেমন ধরো, একেবারে সাম্প্রতিক একটা ঘটনা। বাংলার বিস্তীর্ণ কিছু অঞ্চল ধ্বস্ত হয়ে গেল আয়লায়, মানুষজনের কষ্টের শেষ নেই। বিপুল জায়গা জুড়ে বিপুল সময় জুড়ে ত্রাণ পুনর্জীবন পুনর্বাসনের ত্বরিত ব্যবস্থার দরকার। মানুষ তখন কী করে? অন্য সবকিছু ভুলে যে যার সাধ্যমতো একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম সরকার অপ্রস্তুত, দিশেহারা। অন্য অনেকে সরকারের ওপর দোষারোপে ব্যস্ত। পথচলতি ত্রাণসংগ্রহের কাজে হরেকরকম দলাদলি, সন্দেহ, বিষোদ্গার। তখন এই ভেবে ভয়ানক একটা হতাশার বোধ তৈরি হতে পারে যে, এমন এক বিপর্যয়ের মুখেও পীড়িত মানুষের দুর্ভোগের চেয়ে আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠছে নানা রকমের খুচরো হিসেব। কিন্তু হতাশার সেই একই মুহূর্তে যখন দেখি রাজ্যের এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে কত স্বেচ্ছাসেবী দল নিজেদের জোটানো সামান্য সম্বল নিয়েও চলেছে ত্রাণ কাজে, যখন দেখি রাস্তার কোনও জীর্ণবসনা মহিলা দূর থেকে এগিয়ে এসে আঁচলের খুঁট থেকে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে দেন, যখন দেখি আর্তরা এই ভয়ংকর সময়েও নিজেদের জন্য ত্রাণ না নিয়ে প্রথমে এগিয়ে দিন অন্যদের, নতুন একটা ভরসায় তখন ভরে ওঠে মনটা। একই সময়ে হতে পারে এসব। একই দিনে হতে পারে এই দুই বিপরীত অনুভব। কিন্তু কথা সেটা নয়। কথাটা হল ‘এখন সব অলীক’ আর ‘অবিশ্বাসের বাস্তব’ কি হতাশাবোধেই পৌঁছে দেয় পাঠককে? তাহলে বুঝতে হবে নিজেকে প্রকাশ করায় আমার কোনও গাফিলতি ঘটে গেছে। বইয়ের নামগুলিই একটু বেশি প্রভাবিত করছে না তো? যে-বইয়ের শেষ লেখার নাম ‘আর এক আরম্ভের জন্য’ তা কেন এত হতাশাজনক হবে? ‘এখন সব অলীক’-এর বেশির ভাগ লেখায় আছে আমার যৌবনদিনগুলির কথা, দেখা-কিছু আশ্চর্য মানুষজনের কথা, ইচ্ছে করলেও যাঁদের বা যেসব আর ছুঁতে পারা যাবে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের একতলার বারান্দায় গিয়ে – গোপনে গোপনে যাই প্রায়ই – আজও যদি ভাবি ৫০-৫১ সালের কোনও মুহূর্তকে, তবে তাকে তো অলীক বলেই বুঝতে হবে এখন? যে-কোনও নস্টালজিয়ায় তা হয়। কিন্তু সে তো এখনকার সময় সম্পর্কে কোনও মন্তব্য নয়। কিংবা ধরো ‘অবিশ্বাসের বাস্তব’। সেখানে তো ছিল সম্পর্কগত অবিশ্বাসের প্রবহমানতাকে বুঝে নিয়ে তাকে দূর করবার কিছু কর্মকল্পনা বা স্বপ্নকল্পনা। বিশ্বাসভরেই তো বইটা উৎসর্গ করা হয়েছিল জায়মান এক তরুণ সংগঠনের সম্ভাব্য তরুণ কর্মীদের জন্য। চারদিকে একটা অবিশ্বাসের হাওয়া ছড়ানো আছে, কিন্তু তাকে সরিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে পারস্পরিক সম্পর্কের একটা ভূমি, দেরি হয়ে গেলেও এখনও তা সম্ভব – এইটেই না বলা ছিল সেখানে? আর সেইজন্যেই, দেশের কোণে কোণে, অনেকটা অগোচরে, ছোট ছোট যেসব গোষ্ঠী বা ব্যক্তি আপনমনে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের কথা কখনও কখনও লিখতে করে ‘বটপাকুড়ের ফেনা’য়।
প্র : আপনার কবিতার ভেতর দিয়ে যখন আপনার কাছে পৌঁছতে চায় কেউ – একটা অপরিসীম বেদনাবোধ, বিষণ্ণতা আর অন্ধকার টের পায় সে।
উ : সেটা হতে পারে। তবে খেয়াল করো, তুমি বলছ বেদনাবোধ, বিষণ্ণতা আর অন্ধকারের কথা। আমরা অনেকসময় নিরাশাকে এরই সমার্থক ধরে নিই। সেটা বোধহয় ঠিক নয়। বেদনাবোধ বা বিষণ্ণতা একটা স্টেট অফ মাইন্ড, আর নিরাশা একটা স্টেটমেন্ট। বিষাদ বা বেদনাবোধের মধ্যে অনেক কিছু একসঙ্গে জড়ানো থাকতে পারে। আর অন্ধকার? ভেবে দেখো, কীভাবে বুদ্ধদেব বসুর কবিতাবইয়ের নাম হতে পারে ‘যে আঁধার আলোর অধিক’, বিষ্ণু দে-র বই ‘সেই অন্ধকার চাই’। রবীন্দ্রনাথের বহুতল অন্ধকারের কথা আর না-ই তুললাম এখানে। ওসব তো নিরাশার কথা নয়। অবশ্য বলছি না যে ঠিক ওই আঁধার বা অন্ধকারটাই আমারও কথা। বলতে চাই – একটু আগে যেমন বললাম – আশা-নিরাশায় জড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা সত্তা-অবস্থান তৈরি হতে পারে।
প্র : কিন্তু সেই কবিতা পড়ে যে আপনাকে বুঝতে চাইবে সে আপনার এই মার্জিত সর্বংসহ প্রতিদিনের চেহারাটা মেনে নেবে কেন?
উ : মেনে নেবার দরকার হবে কেন? সে আমার ওই চেহারাটা দেখতেই বা পাবে কেন? যে কবিতা পড়ে, সে তো কবিতা পড়েই কবিকে পায়, যদি দরকার হয় পাবার। কবিব্যক্তিটির সঙ্গে পাঠকের তো মুখোমুখি না হওয়াই ভাল। এ বিষয়ে অবশ্য অনেকেরই সঙ্গে মতের মিল হবে না আমার। কবির সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগের ইচ্ছে বা সুযোগ এতটাই যে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে এখন আমাদের চারদিকে, সে-বিষয়ে কবিদেরও প্রকাশ্য প্রশ্রয়ই আছে। আমার নেই। কিন্তু তোমার প্রশ্নটার মধ্যে আরও দুটো ভাববার দিক আছে। যাকে ‘মার্জিত, সর্বংসহ’ চেহারা বলছ, তার সঙ্গে বেদনাবোধ বা বিষণ্ণতার বিরোধ কোথায়? কিসে? ওই বোধ বা বিষাদ কি কাউকে অমার্জিত কিংবা অধৈর্য করে রাখে নিশ্চিতই? অল্প যে-ক’জন পাঠক আমার কাছে আসেন বা অল্প যেসব পরিচিতজন আমার পাঠক হয়ে যান, তাঁরা অনেকসময় হয়তো আমার ঠাট্টা-মশকরার চেহারাটাও দেখেন, সেটাকে হয়তো বিষাদের বিপরীতই বলা যায়। সেইটে দেখে তাঁদের অসুবিধে হবে বলছ? কিন্তু সব পাঠকেরই কি এই ধারণা যে, বাইরের মানুষটাকে দেখে কোনও লেখকের ভেতরের মনটাকে বোঝা যায়? কোনও কোনও স্রষ্টার ক্ষেত্রে হতেও পারে সেটা, দৈনন্দিনের মধ্যেই সৃষ্টিসত্তাকে ধারণ করে রাখেন তাঁরা, কিন্তু অনেকসময়ই ঘটে না তা। অনেককেই বোঝা যায় না বাইরে থেকে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন? ‘বাহিরে যবে হাসির ছটা/ ভিতরে থাকে চোখের জল’। ওইরকম আর কী। একটা আছে আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্ব, আর একটা অন্তর্গত সত্তা। কবিতার বাসা সেইখানে, সেই সত্তায়। বাইরে থেকে সেটাকে জানা যাবে কেমন করে? দেবই বা কেন জানতে?
প্র : ‘সময়টা একমাত্র আসতে পারে কবির সত্তা হিসেবে’ – এরকম একবার বলেছিলেন। এ-বোধটা কীভাবে তৈরি হল আপনার মনে? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে? নাকি কবিতা পড়ারও ভেতর দিয়ে? কাদের কবিতার কথা এক্ষেত্রে আপনার মনে কাজ করে গেছে?
উ : কোনও কোনও কবির অনুভবে এ-রকম কথার একটা প্রকাশ আছে নিশ্চয়ই। জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ যেমন বলতেন যে সেটা কোনও প্রকট সম্বন্ধ নয়। প্রকটা কথাটা লক্ষ করো। কাব্যতত্ত্ব নিয়ে বলতে গেলেও কয়েকটা কথার উপর কেবলই ভর করতেন তিনি; অন্তঃসার আভা ভাবপ্রতিভা ভাবনাপ্রতিভা। একবার লিখেছিলেন হাড়ের ভিতর বোধ করবার শক্তির কথা। এটা কাউকে হয়তো মনে করিয়ে দিতে পারে ইয়েটসের লাইন, ‘He that sings a lasting song/ Thinks in a marrrow-bone।’ এসব কথাবার্তা পরে আমার ভাবনাকে অনেকটা সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কবিতা বা কবিতাবিষয়ক লেখার মধ্য দিয়েই ওই বোধটাকে পেয়েছি প্রথমে। ওসব পড়তে পাবার অনেক আগেই, লেখা শুরু করবার কিছুদিন পর থেকেই টের পেয়েছি, কোনও কোনও লেখায় শরীরের একেবারে ভিতরদিকে একটা স্রোত বইতে থাকে, আবার কোনও কোনও লেখায় হয় না সেটা। কেন হয় আর কেন হয় না, এইটে ভাবটে ভাবতেই অস্পষ্ট এক ভাবনায় আমি পৌঁছচ্ছিলাম, পরে সেটা স্পষ্টতর হল অন্য অনেকের কবিতা পড়ে। সময় বিষয়ে অনেক সচেতনতা নিয়েও একটি কবিতা কেন স্পর্শ করে না মূলে, অন্য একটি কেন করে, তার একটা উত্তর যেন আছে ওই ভাবনায়। কেউ কষ্ট পাচ্ছে, দরদের চোখে সেটা দেখা আর তা বলাটা এক জিনিস, আর নিজে নিজেই সেটা – সেই কষ্টটা হয়ে-ওঠা, সে হল আর এক কথা। তখনই মনে হয় সমস্ত সত্তা দিয়ে পাওয়ার কথাটা, আড়াল থেকে গোটাটা নিয়ে কাজ করে সেটা।
প্র : কিন্তু চারদিক থেকে নানা সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজে যখন ডাক আসে অথবা ভুল-বোঝাবুঝি হয় কাছের মানুষজনের সঙ্গেও, তখন কী করেন? কবিতা লেখা বা জীবনযাপনের জন্য যে আড়ালের কথা ভাবেন, সেটা ভেঙে যায় না?
উ : একেবারে যায় না তা বলব না, সাময়িকভাবে তো যায়ই। প্রতিবারই এই ধরনের কোনও ডাকে সাড়া দেবার পর, কাজ শেষ হয়ে যাবার পর, অল্পস্বল্প গ্লানির বোধ, এমনকী অপরাধবোধও থেকে যায়। কিন্তু ওই-যে বললাম, ওই একইসঙ্গে জড়ানো থাকে একটা অস্তিবোধও। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, আমি যে-আড়ালের কথা বলি তা কোনও মিনারবাসিতার অন্তরাল নয়। ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে, তার থেকে শ্বাস নিতে আমি ভালইবাসি। ভিড়ের মধ্যে থেকেও মনকে একা রাখা যায়, যদি কেউ চায়। ‘সঙ্ঘে আমি একলা থাকি বটে/ একার পথে সঙ্ঘ টের পাই’। আর নানাজনের ভুল বোঝা? সে তো থাকেই জীবনে। তার হাত থেকে কেই-বা কবে পরিত্রাণ পায়!
প্র : সাহিত্যের রাজনীতি গোটা বিশ্বেই যে-কোনও ভাষায় আছে। আপনি কখনও অনুভব করেছেন এর হিংস্রতা? মুছে দেওয়ার আয়োজন? কীভাবে এর মুখোমুখি দাঁড়াবে একজন? সবার সহ্যশক্তি তো সমান নয়।
উ : না, তা নয়। কিন্তু একজন লেখকের, একজন শিল্পীর সবচেয়ে বড় পরীক্ষাই এই সহ্য করবার ক্ষমতায়। সমাজের প্রকৃতির বিশ্ববিধানের (বা অবিধানের) নিরন্তর বিরোধিতাকে বুকে নেবার ক্ষমতাই হল শিল্পীর ক্ষমতা। ঠিকই, সাহিত্যের রাজনীতি সবসময়েই থাকে, সব দেশে। সেটা হায়ারার্কির দিক থেকেও আসে, আবার অনুভূমিকভাবেও ছড়ানো থাকে সমগোত্রের মধ্যে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তার প্রকৃতিতে আর পরিমাণে কিছু বদল ঘটে, ঝাঁজ বাড়তে থাকে। সন্দেহ, নিন্দেমন্দ, ঈর্ষা, হিংস্রতা সবই ঘূর্ণির মতো ঘুরতে থাকে। অনেকদিন আগে ‘জার্নাল’-এর মধ্যে এর মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো আমার এক ব্যক্তিগত পদ্ধতির কথা বলেছিলাম। সেটা যে সকলের পক্ষে ব্যবহার্য তা নয়, তবু আর একবার বলি। আক্রমণটা বা আঘাতটা যদি ভুল কারণে হয়, যদি অন্যায়ভাবে হয়, তাহলে একদিন-না-একদিন লোকে টের পাবে সেটা, তাই এ নিয়ে আমার বিচলিত হবার দরকার করে না। আর কারণটা যদি যথার্থ হয়, তবে তো লোকের জানাই উচিত সেটা, তা নিয়ে আমার বিচলিত হবার কোনও অধিকার নেই। তাহলে তো কোনওদিক থেকেই আমার কিছু করার রইল না। এসব প্রবোধ মনে রেখেও কখনওই আমার কোনও ধাক্কা লাগে না তা বলব না, তবে অনেকটাই সংবৃত থাকতে পারি, থাকতে চাই, একটা বর্মের মতোই ধরে রাখতে চাই ওই বোধটাকে।
প্র : কবির বর্ম! ‘কবির বর্ম’ বইটায় একটা অন্যরকম প্রসঙ্গ আছে ভাষা আর স্বর নিয়ে। বই থেকে বইতে যদি বদলে যায় কবির বলার কথা আর স্বর, তাহলে তাকে চিনব কীভাবে! বই থেকে বইতে কি বদলানো সম্ভব?
উ : একটা স্তরে সেটা খুবই সম্ভব। যেমন, একটা স্তরে ব্যক্তিমানুষেরও বদল ঘটতেই থাকে। বিশ বছর আগে যে-আমিটা আমি ছিলাম, আর এখন যে-আমি আমি – সে কি একেবারে এক? সময়ের সঙ্গে শারীরিক আর মানসিক বেশ কিছু বদল কি হয়নি তার? সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত আমার যেমন বদল, তেমনই সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কবির কবিতাতেও বদল হতে পারে, সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সে বদল কি এতটাই যে আমাকে আর চেনাই যাবে না মোটে? সেদিক থেকে আমার একটি ধারা-বাহিক আমি আছে। লেখাও তেমনই। বদল হতে থাকে, কিন্তু সে বদলটা চমকে দেবার মতো কিছু না-হওয়াই সম্ভব। ‘আচ্ছা, এবার আমাকে পাল্টাতে হবে’ – জবরদস্তি এ-রকম একটা প্রস্তাব নিয়ে কেউ যে পাল্টান নিজেকে তা হয়তো নয়। ওর জন্য সময় দিতে হয়। অলোকরঞ্জনের ‘যৌবনবাউল’-এ একটা লাইন ছিল, না, ভুল বললাম, ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’তে : ‘কে তবু বলল ট্রামে উঠবার আগে/ এবার কিন্তু আঙ্গিক বদলান’। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই আবার যে বদলে গেল তার আঙ্গিক তা তো নয়। আবার অনেকদিন ধরে অল্প অল্প করে এতদিনে পাল্টেও গেছে ওর স্বর।
প্র : ভাষা, স্বর, দৃষ্টি সর্বোপরি শ্বাসপ্রশ্বাস বই থেকে বইতে বদলে নেবার কথা আপনি কি কখনও ভাবেন না?
উ : না, বড় একটা ভাবি না, অন্তত সচেতনভাবে। বছর দু’-তিন পর পর আমার কবিতার বই বেরোয়, তাতে এমনিই হয়তো পাল্টে যায় কিছুটা, আবার পাল্টায়ও না কখনও। কিন্তু পাল্টাতে হবে ভেবে পাল্টাই না।
প্র : তাহলে ‘দিনগুলি রাতগুলি’ বইটির পর দীর্ঘ সাত-আট বছর কবিতা লেখেননি কেন? বদলের ভাবনায় নয়?
উ : সাত-আট বছর নয়, মুখে মুখে বছরটা একটু বেড়ে যাচ্ছে মনে হয়। বছর চারেক লিখিনি তেমন কিছু। সে-সময়ে এটা ভাবিনি যে, বদলাতে হবে নিজেকে। ভেবেছিলাম, কিচ্ছু হচ্ছে না লেখা, তাই লিখবই না কিছু। শুধু ভেবেছিলাম তা নয়, দু’-একজনকে ওরকম বলেওছিলাম। ওরই মধ্যে কখন টুকরো টুকরো কয়েকটা লাইন লিখেও ফেলতাম এলোমেলো, যাকে মনে হত না-লেখা। এ কিন্তু সন্দীটনের অর্থে সেই না-লেখকের না-লেখা নয়। সন্দীপনের না-লেখা ছিল চলতি লেখার উচ্চারিত প্রতিবাদ। আমি ভাবছিলাম নিরুচ্চার লুকিয়ে ফেলবার কথা।
প্র : আবার কীভাবে ফিরলেন লেখা ছাপানোর জগতে? অতদিন পরে কি লেখা চাইত কেউ? বড়দের সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে এই না-লেখা নিয়ে কথা বলেছেন?
উ : লেখা কেউ চাইলে কখনও কখনও বলতে হত লিখছি না, তা নইলে অবশ্য এ নিয়ে কথা বলিনি কারও সঙ্গে। তবু একজনের কাছ থেকে নিয়মিত চাপ আসতই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ‘কৃত্তিবাস’ তো বেরিয়েই চলেছে তখন, আর ‘কৃত্তিবাস’-এ আমার কোনও লেখা থাকবে না, এ হবার উপায় ছিল না সুনীলেরই জন্য। বিদেশ থেকে একবার লিখেছিলেন (অস্থায়ীভাবে সম্পাদক তখন অন্য কেউ), ‘এবারকার কৃত্তিবাসে আপনার কবিতা দেখলাম না। এ-রকম করবেন না।’ এ ছাড়া চাইত দু’-একটা নিতান্ত খুদে পত্রিকা, যাদের বেশির ভাগেরই আয়ু দু’-তিন সংখ্যা। এইভাবেই টুকটাক করে লেখা হয়ে গেল ‘নিহিত পাতালছায়া’র লেখাগুলি। বুঝতে পারলাম যে কিছুটা পাল্টে গেছে লেখা। কিছুটা নয়, অনেকটাই।
প্র : ‘নিশঃব্দের তর্জনী’ প্রবন্ধটাকে কি বলা যায় ওই ‘নিহিত পাতালছায়া’র ভূমিকা? কোন তাগিদে লেখা ওটা?
উ : বাইরের কোনও তাগিদ ছিল না। কেউ চায়নি, কেউ চেপে ধরেনি, এমনি এমনি একটা গদ্যলেখা হয়ে গেল – জীবনে মাত্র ওই একবারই ঘটেছিল সেটা। ১৯৬৬ সালে। সেই সময়ের মধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছিল ‘নিহিত পাতালছায়া’র প্রায় সব কবিতাই। তাই ঠিক ভূমিকা না বলে ওকে ও-বইয়ের পক্ষে একটা কোনও ম্যানিফেস্টো হয়তো বলা যায়।
প্র : এই প্রবন্ধে কতগুলো লক্ষণের কথা বলা আছে, যার বিরুদ্ধে লড়াই। ‘লোকপুরাণের গুঁড়ো’ মাখা স্বয়ংপুরাণ হতে চাওয়া এক জীবনচর্যা, জীবনানন্দের যা ছিল পরিধান তা দিয়ে ‘আসবাবের মতো সাজানো’ কবিতার ঘর, ‘সুলভ বড়োবাজার’-এ গর্বহীন এক লেখকসমাজ – এসব কি তখনকার কবিতার লক্ষণ ছিল আপনার কাছে?
উ : খানিকটা তাই। তবে সে-কবিতার অন্তর্গত তখন তো আমিও। এখানে একটা তথ্য বলি। প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছিল কোথায় জানো? খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে তখন বেরোতে শুরু করেছে পনেরো দিনের ‘দৈনিক কবিতা’, যাকে হয়তো-বা একটু ঠাট্টা করবারই জন্য সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে ‘কবিতা ঘণ্টিকী’, ঘণ্টায় ঘণ্টায় কবিতা-পত্রিকা! সেই ‘দৈনিক কবিতা’য় একটা লেখার জন্য চাপ দিতে এলেন তারাপদ রায়। ওঁকে হতবাক করে সঙ্গে সঙ্গে হাতে তুলে দিলাম লেখাটা। ‘দৈনিক কবিতা’য় ‘নিঃশব্দের তর্জনী’ – এর মধ্যে একটা আয়রনি হয়তো আছে।
প্র : তাহলে কীভাবে পরবর্তী সময়ে এই সময়কার লেখার মহিমা খুঁজে পেলেন?
উ : মহিমা কিন্তু তখনও খুঁজে পেয়েছিলাম। একাধিক গদ্যে সেই সময়ের নতুন লেখালেখি নিয়ে গ্রহণশীল কথাবার্তা বলেছি তখনও। শুধু বুঝতে পারছিলাম না যে, আমি ঠিক ও পথে চলতে চাইছি না। আরও একটা কথা আছে এ প্রসঙ্গে। সমসময়ে মূল লেখার চারপাশে এমন অনেক কিছু ভাসতে ভাসতে একসঙ্গে এগোতে থাকে যে, প্রথমে চোখে পড়তে চায় পিণ্ড-পাকানো ঘূর্ণিলাগানো স্রোতটাই। অবান্তর অংশটা ঝরে যেতে থাকে একটু একটু করে, অন্যদের চোখে ঠিকঠাক চেহারাটা বেরিয়ে আসতে থাকে তখন।
প্র : ‘নিঃশব্দের তর্জনী’তে লিখেছিলেন, ‘এখন ইচ্ছে করে যেমন-তেমন বলতে, খুব আপনভাবে কাঁচা রকমে, খুব ছোটো আর খুব সহজ’! – এখানে ‘সহজ’ বলতে কী বুঝিয়েছিলেন? ‘জলের মতো সহজ হব’ বলেছেন কবিতায়। সেই ‘সহজ’ই বা কী? কবিতার সহজ কি ঠিক ততটা সহজ?
উ : নয় তো। লিখেও তো ছিলাম ‘সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়’। তখন যেটা বলতে চেয়েছিলাম তা হল নানা রকমের চমৎকৃতি থেকে বেরিয়ে আসার কথা। শব্দের ভার, ছবির জৌলুস, ছন্দের দোল – এসব থেকে নিজেকে যথাসম্ভব সরিয়ে নেওয়ার কথা। অন্ধকারে পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকতে পারে দু’জন, মাঝে মাঝে আলতো দু’-একটা কথা বলে ফেলে, সেইরকম। দৈনন্দিন কথাবার্তার চাল, তার শ্বাসপ্রশ্বাস, যথাসম্ভব তার কাছাকাছি থেকে কথা বলা। এসবকেই বলেছিলাম সহজ। কিন্তু তার থেকে যে-অনুভূতিটা পৌঁছয় তাতে হয়তো অনেক জট-জটিলতা থাকতে পারে। আসলে, ভাষার বা কথার নানা রকমের তল তৈরি হতে থাকে তখন। এক দিকে সহজ সীমায় সময়টাকে ধরে রাখতে পারে যে-ভাষা, সে কিন্তু অন্য দিকে আবার গড়িয়ে যেতে পারে অনেক দূরে।
প্র : সময়চিহ্ন ধরবার জন্য এখন অনেকেই সচেতনভাবে নিয়ে আসছেন প্রচুর হিন্দি বুলি আর ইংরেজি গালিগালাজ, টেলি সিরিয়াল, টেলিশো, এফএম রেডিও – এইসব থেকে খুঁজে পাওয়া। ওই ভাষাগুলোর সত্যিকারের স্পন্দ আর চালচলন বড়-একটা জানা থাকে না আমাদের। কেমন করে সচেতন থাকবেন লেখক, শব্দ দিয়ে বা কানে শোনা এইসব বুলি দিয়ে সময়কে ধরবার চেষ্টায়?
উ : খুব বেশি চেষ্টা করে এটা হয় বলে মনে করি না। এ খানিকটা প্রবণতার ব্যাপার। বিশেষ বিশেষ কবির ক্ষমতার ব্যাপার। হিন্দি বা ইংরেজি যেসব বুলি দৈনন্দিনে ঢুকে গেছে – তা টেলিশো থেকেই হোক বা অন্য কোনও সূত্রেই হোক – কবিতার মধ্যে তা তো চলে আসতেই পারে, আসবারই কথা। সমসময়ের সঙ্গে একটা যোগ তো রাখতেই চায় কবিতা। সমস্যা হল, যদি কারও মনে হয় এটা তাকে করতেই হবে, কেননা এই হল একটা আধুনিকোত্তর লক্ষণ, তাহলে একটা জবরদস্তির ব্যাপার ঘটতে পারে লেখায়। কবিতা পড়ে কিন্তু বোঝা যায়, কোনটা স্বভাবত আসে আর কোনটা-বা জোর করে চাপানো। স্বতঃস্ফূর্ত এক জৈব সম্পর্কে যদি জড়ানো থাকে সবটা, তবে সমকালীন বুলি কবিতার একটা শক্তিই হতে পারে।
প্র : আপনি একবার লিখেছিলেন, ‘মারের জবাব মার’। ওই একবারই অবশ্য। আজও কি বিশ্বাস করেন ও কথাটায়? কীভাবে এসেছিল লাইনটা?
উ : কীভাবে এসেছিল তা ঠিক মনে নেই এখন। তবে কথাটার মর্মে এখনও আমার বিশ্বাস নেই, তখনও ছিল না। তবে লিখলাম কেন? প্রথমত, কবিতার সব কথাই কিন্তু রচয়িতার নিজের কথা নয়, নাট্যচরিত্রের কথা যেমন নয় নাট্যকারের কথা। কবিতায় আমার ও তোমার শব্দগুলির দ্যোতনা মুহুর্মুহু পাল্টে যেতে পারে। আর দ্বিতীয় কথাটা হল, গোটা কবিতা থেকে একটা দুটো লাইনকে আলগা করে নিয়ে ভাবলে অনেকসময় একটা গোলমাল হয়ে যায়। ধরো, এই যে কবিতাটা, দু’-লাইন দু’-লাইনে গাঁথা বোধহয় দশ-বারোটা লাইন, যার মধ্যে কয়েকবারই ধুয়োর মতো আসছে ওই ‘মারের জবার মার’, যে-কবিতার নাম ‘স্লোগান’ – তার শেষ দুটো লাইন মনে আছে তো? সেটা ছিল ‘কথা কেবল মার খায় না কথার বড়ো ধার/ মারের মধ্যে ছল্কে ওঠে শব্দের সংসার।’ তখন কি কথা দিয়ে বা শব্দ দিয়ে মারের একটা পাল্টা শক্তিই তৈরি হল না? হিংসা-রাজনীতির যে-হাওয়া বইছিল সেই সত্তর দশকের গোড়ায়, ওইসব স্লোগানের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল কত ‘ব্যক্তি’ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা, সেই বোধ থেকেই কিন্তু লেখা হয়েছিল ওই কবিতা।
প্র : ‘ব্যক্তি’কে ডাক দিতে পারে, গত শতাব্দীর ভারতে এমন কোনও রাজনৈতিক সদিচ্ছা খুঁজে পেয়েছেন? যেখানে বিশ্বাস রাখা যায়? সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্বতা নিয়ে যেখানে জড়ো হতে পারে?
উ : হতে পারত, প্রাথমিকভাবে পেরেওছিল, গাঁধীজির নেতৃত্বে। গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে একসঙ্গে ডাক দেবার বা জড়ো করবার কাজে অনেকখানি এগোতে পেরেছিলেন গাঁধী। তাঁর রাজনীতিতে ছিল একটা ব্যক্তিসম্বন্ধের কথা, ছিল ব্যক্তিত্বের বিকাশসূত্রে গ্রামসমাজের বিকাশ আর সেই সূত্রে গোটা দেশের বিকাশের কথা। মানুষে মানুষে একটা ভালবাসার কথা যে রাজনীতির ভূমিতে দাঁড়িয়েও বলা যায়, আর বলা যায় বেশ নিচু গলাতেই, এইটে ছিল ওই রাজনীতির একটা মহিমার দিক। কিন্তু এসব হল নেতার সদিচ্ছার কথা, স্বপ্নের কথা। কিন্তু মুশকিল যে, কর্মপ্রণালীতে এর অনেকটাই রূপায়িত হতে পারেনি, বরং সেখানে ‘ব্যক্তি’র ওই ‘নিজস্বতা’র চিহ্ন অনেকটাই গেছে মুছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সেই চিন্তাটাকেই সঙ্গত মনে হয়, ‘সত্যের আহ্বান’-এ গাঁধীজির যে-সমালোচনা তিনি করেছিলেন। ‘মুক্তধারা’ নাটকের ধনঞ্জয় তার অনুগামী মানুষজনের বিষয়ে একবার দুঃখ করে বলেছিল, ‘ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি’ – সেইটেই হতে পারত গাঁধীজিরও কথা।
প্র : রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আপনি সব সময়েই বলেন, কিন্তু সব প্রসঙ্গে বলেন না। যেমন, ছোটগল্প নিয়ে বলেননি কিছু। এর কারণ?
উ : বিশেষ কোনও কারণ নেই, কেউ নিশ্চয়ই তেমন চেপে ধরেননি কখনও। আবার, একেবারে যে লিখিনি তা-ও বোধহয় নয়, ‘নির্মাণ আর সৃষ্টি’-র মধ্যে আছে হয়তো একটু-আধটু।
প্র : আপনার কি নিজের মতো করে রবীন্দ্রভাবনার কোনও অভিমুখ আছে?
উ : বিশেষ কোনও অভিমুখ নিয়েই শুরু করেছিলাম এমন নয়, তবে গোড়ার দিকে ঝোঁক ছিল আঙ্গিকটা লক্ষ করবার। নাটক গান আর সৃষ্টিশীলতার শেষ দশ বছর, বারেবারেই নজর গেছে সেখানে। কিন্তু আলগা-আলগা ভাবে নয়। সবটাকে মিলিয়ে। এইখানটায় আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতন ভাবুকের সঙ্গে একটা মতভেদ হত অল্পস্বল্প। তর্ক হত। সে-তর্কের একটা দিক ছিল কবিতা পড়ার পদ্ধতিগত প্রশ্নে। কিন্তু অন্য দিকে, উনি ভাবতেন ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই। আর আমার মনে হত এক বিস্ময়কর ঐক্যসূত্রে এই মাধ্যমগুলি জড়ানো। ফলে কোনও একটা বিষয়ে বিচার করতে গেলে আরও কয়েকটি তার মধ্যে চলে আসে অনিবার্যতই, এ রকম মনে হত। কেবলমাত্র সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমই নয়, তাঁর কাজের জগতের ভিন্ন ভিন্ন দিকও – যেমন পল্লিসংগঠন, শিক্ষাসংস্কার, রাষ্ট্রনীতি – এসবেরও মধ্যে কাজ করে গেছে একই মূলসূত্র। সূত্রটিকে এক কথায় রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন। বলেছিলেন যে আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনাই তিনি নিরন্তর ধরে রাখতে চেয়েছেন তাঁর জীবনে। একে তিনি বলেছিলেন, ‘আবরণ মোচনের সাধনা’। আধুনিকতার বিচারের সঙ্গে সঙ্গে মূলত ওইটেকেই আমি লক্ষ করতে চেয়েছিলাম আমার লেখায়। দেখতে চাইছিলাম তাঁর জীবনচর্যা বা শিল্পচর্চায় ‘আমি’ কীভাবে গিয়ে পৌঁছতে চায় ‘আত্ম’-র কাছে। সেইখানে তাঁর আধ্যাত্মিকতার ভিন্ন রকম একটা মানে পাওয়া যায়।
প্র : ‘নৈবেদ্য’ অথবা ‘গীতাঞ্জলি’ যখন পড়ি, তখন কিন্তু মনে হয় একটা বড় কোনও প্রবল অস্তিত্ব আছে, যার ওপর সমস্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করা চলে। এ-রকম অনুভব কি আপনারও আছে?
উ : বিশ্বাস ন্যস্ত করা চলে, অন্তরালের এমন কোনও প্রবল অস্তিত্বের কথা আমার অনুভবে আসে না। গোটা ব্রহ্মাণ্ডের মূল একটা শক্তিকেন্দ্র যে আছে, সে বিশ্বাস তো করতেই হয়। সে-শক্তিপ্রবাহের সঙ্গে মানসিক একটা সংযোগ ঘটতে থাকে অনেক সময়ে, যার থেকে গড়ে ওঠে একটা কোনও অলক্ষ্য বেদনাবোধ বা অপার বিস্ময়বোধ। কিন্তু সে যে ব্যক্তি-আমাকে কোথাও কোনও আশ্রয় দেবে এমন কোনও বিশ্বাস আমার নেই। সে অস্তিত্বের কোনও নৈতিক বিধানে বিশ্বাস নেই আমার। এখানে বরং আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাবনার আমি সহমর্মী। সর্বশক্তিময় সর্বকল্যাণময় কোনও বিধাতায় বিশ্বাস ছিল না আইয়ুবের, আমারও নেই। অর্থাৎ, সেই অর্থে আমাদের কোনও ধর্ম নেই।
প্র : যেখানে যখন আছি সেইখানটাকেই শেকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা একটা অন্য ধর্মের কথা আপনি বলেন। আর তার জোরটা আছে ভালবাসায়। এই সংলগ্ন হয়ে থাকার প্রেম সব সময় থাকে মনে? ছিঁড়ে যায় না?
উ : সে তো যায়ই। বারেবারেই ছিঁড়ে যায়। আর সেইজন্যেই বারেবারে নিজেকেই মনে করিয়ে দিতে হয় কথাটা, ভেতর থেকে একটা শক্তি পাবার জন্য। যদি ছিঁড়ে না যেত, স্থির হয়ে থাকত সব, একটা সিদ্ধান্ত-অবস্থানে পৌঁছে যেত মন বা অস্তিত্ব, মনে হয় না তাহলে আর কবিতা লিখবার দরকার হত। ছিঁড়ে যাওয়া আবার জুড়ে নেওয়া আবার ছিঁড়ে যাওয়া – এই ভাবেই চলতে থাকে অবিরত।
প্র : ‘জলে ভাসা খড়কুটো’য় একেবারে কথা বলার গদ্যচালে একটা ভাসমান সংলাপের মতন কথা চলেছে। খুব গোপন কথা। শরীর দিয়ে ভালবাসবার কথা। একেবারে শেষে আসছে মিশ্রকলাবৃত্তে লেখা চার টুকরো – ছিঁড়ে যাচ্ছে স্রোতটা। কোন পরিবেশে কীভাবে শুরু হয়েছিল ওই লেখা?
উ : পঁচানব্বই সালে কয়েকদিনের জন্য বাংলাদেশ ঘুরে আসবার কিছুদিন পরে হঠাৎই হয়ে উঠতে থাকে ওই লেখাগুলি। মনে মনে একই সঙ্গে খুব একটা আসক্তি আর মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলাম তখন, যেন মিশে গিয়েছিলাম দেশের জলমাটির সঙ্গে। তারপর একসময় থেমে গেল প্রবাহটা, ঠিকই, ছিঁড়ে গেল। এটা ঠিকই লক্ষ করেছ যে মিশ্রকলাবৃত্ত এসে ওখানে একটা যতিচিহ্ন যেন তৈরি করে দিল। আবার কোনও নতুন প্রবাহের জন্য প্রতীক্ষা।
প্র : আপনার শেষ কবিতার বইটির শেষ অংশটায় একটা রাজনৈতিক সংঘর্ষের তুঙ্গ মুহূর্ত যেন ভালবাসা ভরা দেশ-শরীরে মিশে যাচ্ছে। আপনি কি তেমন কোনও আশ্রয়ের কথা ভাবেন আজ?
উ : সকলেই একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছে, জন্মমুহূর্ত থেকে যে-কোনও মানুষের সেইটেই সবচেয়ে বড় সন্ধান, সেই হাহাকারই সবচেয়ে বড় হাহাকার। সবাই হয়তো সে-বিষয়ে সচেতন থাকে না সবসময়। আবার থাকেও অনেকে। বিশেষত নির্জন একাকিত্বের মুহূর্তগুলিতে। কয়েকদিন আগেই একটা লেখায় বলেছি : ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতের একটা পরবাস-সম্পর্কে বাঁধা আছে মানুষ। আজীবন পরবাসী সেই মানুষ চিরকালই শুধু আশ্রয়ভিখারি। কেউ তা জানে, কেউ-বা জানে না।
Have your say
You must be logged in to post a comment.
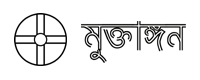
২০ comments
রায়হান রশিদ - ১৮ আগস্ট ২০০৯ (৫:৫৫ অপরাহ্ণ)
ধন্যবাদ সুমন দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারটি কষ্ট করে তুলে দেয়ার জন্য। মুক্তাঙ্গনে কবিকে নিয়ে বাঁধনের ফটোব্লগ প্রকাশিত হয়েছে অবধি এর অপেক্ষাতেই ছিলাম। সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নগুলো যেমন অন্তর্ভেদী, তেমনই গভীর কবির উত্তরগুলো। খুবই উপভোগ্য।
পড়তে পড়তে প্রায় এক যুগ কিংবা তারও আগে চট্টগ্রামে নির্মাণ-এর এক পাঠচক্রে কবির সাথে এক সন্ধ্যা মনে পড়ছে। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে। মনে পড়ছে, কবির সাথে গল্প শেষে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমরা আলোচনা করছিলাম কবির ‘ভদ্রতাবোধ’ এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে। সুক্ষ এক ধরণের দৃঢ়তার আচ্ছাদনে মোড়া এ ধরণের ভদ্রতাবোধ আজকাল আর তেমন চোখে পড়ে না। লেখক তো অনেকেই আছেন, সত্যিকারের সজ্জন ভদ্রলোক কয় জন আছেন? কত কিছু শেখার আছে এই মানুষগুলোর কাছ থেকে। এই সাক্ষাৎকারটি পড়ে আবারও ভাল লাগলো অনেক আগের শঙ্খ ঘোষকে নতুন করে খুঁজে পেয়ে।
ভালো কথা। সেই আড্ডায় কবিতা পাঠ পর্বে কবির স্বকন্ঠে কিছু কবিতা রেকর্ড করা হয়েছিল। মাইক্রো-ক্যাসেটটি হারিয়ে যায়নি তো? যদি এখনো থাকে সেটা, কোনভাবে ডিজিটাল ফরম্যাটে সেটা পাল্টে নিয়ে এখানে তুলে দেয়া গেলে মন্দ হোতো না।
দ্রষ্টব্য: সময় পাল্টেছে এখন। ‘ভদ্রলোক’ শব্দটা আজকাল আর প্রশংসা অর্থে উচ্চারিত হতে শুনি না তেমন। ‘সুশীল’ ইত্যাদি বিষয়ের রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপট মিলিয়ে অনেক শব্দেরই মানে পাল্টে গেছে এখন। সেদিন তো একজন “ভদ্রতাবোধ” শব্দটা উল্লেখ করতেই এমনভাবে তাকালেন যেন বিরাট কোন গর্হিত কাজ করে ফেলেছি। ‘উত্তরাধুনিক মূ্ল্যবোধ’ এর বদহজমজাত অভদ্রতা, অবিনয়, ব্যক্তি আক্রমণ, অশ্রদ্ধাবোধ, মাতবুরেপনা, নিয়ন্ত্রণপ্রিয়তা যেখানে যুগের বিচারে চৌকশ আর চোখা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক, সেখানে দাঁড়িয়ে কবি শঙ্খ ঘোষকে আবারও একজন ‘ভদ্র সজ্জন’ মানুষই বললাম, কিছুটা ভয়ে ভয়ে।
ধন্যবাদ সুমন। ধন্যবাদ সুমন্ত।
মাসুদ করিম - ২৪ আগস্ট ২০০৯ (৩:৩০ অপরাহ্ণ)
ভদ্রতাবোধ সভ্যতার সবচেয়ে বড় পরিচয়চিহ্ন। কিন্তু নানা দুর্বিপাকে ভদ্রতাবোধ প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের সিভিল সোসাইটি বা যাকে আমরা এখন উভয় বাংলায় সুশীল সমাজ বলছি, কখনো কখনো আবার উঁচুদরের বাংলা পত্রিকা বা প্রচার মাধ্যম বিদ্বজ্জন বলছে, তাদের নানা কর্মকাণ্ডে, ব্যাপক অর্থে সুশীল শব্দটি এখন খুবই সন্দেহজনক একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। শঙ্খ ঘোষের সাথে আপনার ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় সন্দেহাতীতভাবেই একজন ‘ভদ্র সজ্জন’-এর ছাপ রেখে গেছে আপনার মনে। আমার সাথে শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় নেই কিন্তু যেই ‘রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপট’-এর কথা আপনি বলেছেন, সে কারণেই আজ শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্গার্থে ‘সুশীল’ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে; ঠিক আমাদের দেশে আমরা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহার করি। নাৎসি পরবর্তী জার্মানির তরুণ লেখকরা যেমন অনেক মহত্ব নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন, তেমনি ঠিকই বলেছেন ‘অনেক শব্দেরই মানে পাল্টে গেছে এখন’।
রেজাউল করিম সুমন - ২৬ আগস্ট ২০০৯ (১২:৪০ অপরাহ্ণ)
@ রায়হান
১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারির সেই উদ্দীপনা-ভরা দিনগুলোর কথা কী করে ভুলি! ’৯৫-এর পর সে-বারই শঙ্খ ঘোষ আবার এলেন চট্টগ্রামে।
সে-বারের কয়েক দিনের ঘটনা তোর স্মৃতিতে একাকার হয়ে গেছে বলে হচ্ছে। শঙ্খ ঘোষের কিংবা কবিকন্যা সেমন্তীদির সঙ্গে একটু নিরিবিলিতে আলাপ বা আড্ডা হয়েছিল টুলুদার বাড়িতে; সেখানেই উঠেছিলেন তাঁরা। আর কবির স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠ রেকর্ড করা হয়েছিল ফুলকি-তে। আরো অনেকের সঙ্গে আমরা নির্মাণ-এর তরুণরাও ছিলাম সেই অনুষ্ঠানে। রেকর্ডার হাতে মুনিরের সেদিনের অনুপ্রাণিত মুখ কখনোই ভোলার নয়। আমাদেরই পছন্দের কবিতাগুলো একে একে পড়ে শোনাচ্ছিলেন শঙ্খ ঘোষ! আর শেষদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কবির সাক্ষাৎপ্রার্থী কেষ্টবিষ্টুদের তফাতে রেখে নির্মাণ-এর জন্য তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল অধুনালুপ্ত সাহিত্য নিকেতনে। সেদিন সন্ধ্যায় তুই কী কারণে হাজির থাকিসনি এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না।
মাইক্রো-ক্যাসেটটা কারো হাতে পড়ে নষ্ট হতে পারে, এই ভয়ে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এখন নিজেই আর খুঁজে পাচ্ছি না!
২
ক’দিন আগে যখন শিল্পী শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তখনও উঠেছিল শঙ্খ ঘোষের প্রসঙ্গ। কবির নাম শুনে সেদিন শিল্পীর প্রথম প্রতিক্রিয়াই ছিল এরকম : ‘ভদ্রলোক! … ভদ্রলোক! … ভদ্রলোক!’ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শাহাবুদ্দিন কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন, তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল শঙ্খ ঘোষেরই বাসায়।
নিজাম উদ্দিন - ১৯ আগস্ট ২০০৯ (৮:৩২ অপরাহ্ণ)
পড়লাম। ভালো লাগল বলে কিছু অংশ দ্বিতীয়বার পড়লাম। শঙ্খ ঘোষের বাচনে একই সাথে মগ্নতা আর বিমূর্ততার কেমিস্ট্রি আছে। লেখাটি পড়ে আবার ফোন করে কবির সাথে কথা বলার ইচ্ছে জাগল।
এখন কী করি?
মুয়িন পার্ভেজ - ২২ আগস্ট ২০০৯ (৭:৪৯ পূর্বাহ্ণ)
কবির সাক্ষাৎকার আমার কাছে সবসময়েই আগ্রহের বস্তু, কিন্তু বেশির ভাগ সাক্ষাৎকারই — আমার ক্ষুদ্র গণ্ডির প্রেক্ষিতেই অবশ্য — প্রশ্নবাজদের উটকো প্রশ্নবাণে জর্জরিত-নিঃশেষিত হয়ে যায়। সাজানো ফর্দের মতো নিঃসার সাক্ষাৎকার, যা পাঠপীড়ন ছাড়া অন্য কোনো বিভা তৈরি করতে পারে না; যেমন, শামসুর রাহমান বা হুমায়ুন আজাদকে সাধারণত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েই বলতে হত বেশি-বেশি — প্রশ্নকর্তার পাঠপ্রস্তুতির অভাব এর কারণ হতে পারে, বা দুরভিসন্ধিই, ফলে, জীবনযাপন ও সাহিত্যচর্চার আলো-অন্ধকারময় জায়গাটি অধরাই থেকে যায়। সুমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অশেষ ধন্যবাদ এজন্যই যে, কবির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন নিছক প্রশ্নোত্তরপর্বে পর্যবসিত হয়নি।
২
প্রকাশিত সমালোচনা (কিয়দংশে ব্যক্তিবিদ্বেষ) প’ড়ে কিছু কাছের মানুষকে উন্মত্ততা প্রকাশ করতে দেখি বিভিন্নভাবেই। তাদের জন্য বিশল্যকরণী হতে পারে শঙ্খ ঘোষের এই আপ্তবাক্য :
সত্যিই তো, শুধু কলম থাকলেই চলে না, প্রত্যেক কবিরই উচিত ‘বর্ম’টাকেও আত্মস্থ ক’রে নেওয়া।
৩
‘ছন্দ মানি না’ ব’লে যে-ছন্দোমূর্খ কবিদল কবিতার উঠোনে আগাছা বাড়িয়ে তুলছেন নিরন্তর, তাঁরা কি কখনও বুঝতে পারবেন এই ‘কোনও নতুন প্রবাহের জন্য প্রতীক্ষা’র যতিচিহ্নটুকু?
ধন্যবাদ রেজাউল করিম সুমনকে, যক্ষশ্রমে যাঁর জুড়ি নেই!
মাসুদ করিম - ২৩ আগস্ট ২০০৯ (১২:২৩ অপরাহ্ণ)
আমরা যারা ছন্দ না জেনে কবিতা লিখছি, এবং অতীতেও যারা ছন্দ না জেনে কবিতা লিখেছেন, আবার যারা ভবিষ্যতেও ছন্দ না জেনেই কবিতা লিখবেন, আমরা সবাই আগাছা বাড়াব নিরন্তর, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই আগাছাগুলোর ভেতর যদি কবিতা থাকে, এবং সেই কবিতা যদি ছন্দতাড়িতরা খুঁজে না পান, তবে কি কবিতারই ক্ষতি হবে না?
মুয়িন পার্ভেজ - ২৪ আগস্ট ২০০৯ (৮:২৭ পূর্বাহ্ণ)
ধন্যবাদ, মাসুদ করিম। ‘ছন্দতাড়িত’ কথাটি অন্য এক বিতর্কচত্বরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ছন্দকৈবল্য কবিতার শিল্পশর্ত নয়। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের স্বতন্ত্র সৌন্দর্য স্বীকার ক’রে নিয়েছেন মহৎ কবিরা; দেখিয়েছেন, সাভরণ কবিতার সঙ্গে নিরাভরণ কবিতাও ব্যঞ্জনাগুণে স্বাবলম্বী হতে পারে। কিন্তু, ধরা যাক, শঙ্খ ঘোষের ‘বাবুমশাই’ বা ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ কবিতাদু’টি কি অনুবাদযোগ্য অক্ষরবৃত্তে? কিংবা মাত্রাবৃত্তের গলুইয়ে দুলে উঠতে পারে বুদ্ধদেব বসুর ‘চিল্কায় সকাল’? বলার কথা নয়, কথা বলার ভঙ্গিতেই মূলত তৈরি হচ্ছে প্রকাশপার্থক্য। ‘আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য’, বলছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। কিন্তু বহু তরুণ কবির ছন্দোবিশ্বাস আজকাল যেভাবে ধরা দিচ্ছে, তাতে আশাভঙ্গই ঘটছে, বলতে হয়। দৈনিক সমকাল-এর সাহিত্যসাময়িকী কালের খেয়া-আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বিজয় আহমেদ বলছেন :
(‘সমকালীন কবিদের চোখে সমকালীন বাংলা কবিতা’, কালের খেয়া, ১৪ আগস্ট ২০০৯, পৃ. ১০)
এর আগে দৈনিক প্রথম আলো-র সাহিত্যসাময়িকী-আয়োজিত অন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকে বলছেন আফরোজা সোমা :
(‘তরুণ লেখকদের সাহিত্য’, সাহিত্যসাময়িকী, ২০ মার্চ ২০০৯, পৃ. ৩)
তারিক টুকুর মন্তব্য আরও ভয়াবহ :
(‘তরুণ লেখকদের সাহিত্য’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩)
ছন্দের বারান্দা বইয়ের ভূমিকায় শঙ্খ ঘোষের যে-নির্দেশনা, ‘ছন্দোমুক্তি নয়, ছন্দে মুক্তি’ — কথাটি বোধ হয় গুলিয়ে ফেলছেন কতিপয় তরুণ কবি। মনে পড়ছে অনেকদিন আগে পড়া দেশ পত্রিকার এক মনোরম প্রচ্ছদবিতর্কের কথা : ‘কবির লড়াই’। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তর্কে মেতেছেন কবিতা নিয়ে, সঙ্গে ‘দোহার’ বা সঞ্চালক হিশেবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। শক্তি মোটামুটি ছন্দকৈবল্যবাদী; সুনীল বলছিলেন তরুণ কবিদের উদ্দেশে, যে, ছন্দটা জানা থাকা দরকার, ব্যবহার করো বা না করো, ‘কিন্তু নিরস্ত্র হয়ে এসো না।’
আর, ‘আগাছাগুলোর ভেতর’ থেকে কবিতা? এ তো সোনার পাথরবাটি! স্বরবৈচিত্র্যের খাতিরেই ছন্দকে করায়ত্ত রাখতে হয়, কিন্তু ছন্দোমূর্খতা যদি স্বরকেই প্রলাপে পরিণত করে, তাহলে তা গাছকেও কাটবে, আগাছাকেও।
আসমা বীথি - ২৪ আগস্ট ২০০৯ (৮:৪৮ অপরাহ্ণ)
ছন্দোমূর্খ কবি-দলের প্রসঙ্গ যেন কিছুটা অযাচিতভাবেই এল।
ছন্দকে উড়িয়ে দেওয়ার ধৃষ্টতা বাহাদুরি নয় মোটেও; তবে যে ছন্দোমূর্খতা স্বরকে প্রলাপে পরিণত করে, সেটিও কী ধর্তব্যের মধ্যে পড়বার কথা?
এই দুই বৈপরিত্যের সমাধান বোধহয় একটি ভাল বা উত্তীর্ণ লেখার মধ্য দিয়ে বিবেচনা করা ভাল। এখন ভাল বা উত্তীর্ণ লেখার মান কীভাবে নির্ণয় করা যাবে?এরও একটা মীমাংসা শঙ্খের আলাপে ফুটে ওঠে:
ভাল লেখার মধ্যে লেখকের মানসিক একটা স্বচ্ছতা থাকে। আর থাকে কোনও একটা বিশ্বব্যাপ্ত বোধের ইশারা। জীবনটাকে, গোটা জগৎটাকে নতুন-একটা চোখে দেখতে পাবার ক্ষমতা, সে-জীবন বা সে-জগৎ বিষয়ে কোনও-যে সিদ্ধান্ত মেলে তা হয়তো নয়, একটা প্রশ্ন জাগিয়ে তোলাই বড় কথা। সেই প্রশ্ন দিয়ে আমাকে আলোড়িত করে তোলা, একটা অভিমুখীনতা তৈরি করা, এইটেই আসল।
মুয়িন পার্ভেজ - ৩১ আগস্ট ২০০৯ (৪:২৮ পূর্বাহ্ণ)
শঙ্খ ঘোষ ‘ভাল বা উত্তীর্ণ লেখার’ দু’টি শনাক্তচিহ্ন দেখিয়েছেন : একটি ‘লেখার মধ্যে লেখকের মানসিক একটা স্বচ্ছতা’, অন্যটি ‘একটা বিশ্বব্যাপ্ত বোধের ইশারা’। ‘বিশ্বব্যাপ্ত বোধের ইশারা’ বোঝা গেলেও ‘লেখকের মানসিক স্বচ্ছতা’ কীভাবে বুঝবেন পাঠক? ভালো কবিতা কি বায়বীয় বস্তু? শব্দই কবিতার কঙ্কালকাঠামো এবং ব্যঞ্জনা তার প্রাণভোমরা। শব্দের আশ্রয়ে একটি ‘বোধের ইশারা’ নিশ্চয়ই সঞ্চারিত হবে পাঠকের মনে — নির্বোধ কবিতাকে ভালো তো বলবেন না কেউই। ব্যক্তিগত বোধকে ’বিশ্বব্যাপ্ত’ ক’রে তুলতে পারা অবশ্য বড় কবিত্বেরই লক্ষণ। কিন্তু শুধু এই মানদণ্ড দিয়ে কি সব কবিতার বিচার সম্ভব? শামসুর রাহমানের একটি সনেট পড়া যাক :
(মাতাল ঋত্বিক, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৬৩)
কবিতা লেখার জন্য যে-মগ্নতা ও তৎপরতা দরকার, তার সঙ্গে রূপকার্থে সঙ্গমের অনুষঙ্গ তুলনা করেছেন কবি। আর এই কাব্যসাধনা যার জন্য উৎসর্গিত, সেই দয়িতাই অনুপস্থিত। কবিতায় বিরহবোধ অত্যন্ত সহজলভ্য ও প্রাচীনতম, কিন্তু ঠিক এই ভঙ্গিতেই কি বিরহের কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ বা বিনয় মজুমদার? জগজ্জীবন সম্পর্কেও বা এখানে আছে কোনো প্রশ্নের আলোড়ন? স্বরপার্থক্যগুণেই একটি কবিতা বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে; শুধু আধুনিক-উত্তরাধুনিক মতবাদে সিদ্ধ কিংবা দুর্বোধ্যগম্ভীর হলেই কবিতা ভালো আর না হলে মন্দ — এমন বিবেচনা, শামসুর রাহমান-কথিত ‘পল্লবগ্রাহিতারই নামান্তর’, বলা যায়। বিচিত্র ঢঙের ও রসের কবিতা আস্বাদনের জন্য চাই বোধের বিকেন্দ্রীকরণ।
বহু তরুণ কবি, যাঁরা ছন্দোবিরোধিতায় কণ্ডূয়নের সুখ খুঁজে পান, তাঁদের কবিতা উদ্ধৃত ক’রে দেখানো যায় যে ছন্দচৈতন্যের অভাবেই পদে-পদে স্খলন ঘটছে। মোটামুটি সুন্দর গরু হলেই কোরবানি চলে, তবু শিংভাঙা গরুটি কেউ কিনতে চায় না। সব কিছু নিয়েই — শব্দ-ছন্দ-ব্যঞ্জনা — একটি উত্তীর্ণ কবিতা, গোবিন্দচন্দ্র দাস যেমন বলছেন, ‘আমি তারে ভালোবাসি রক্তমাংসসহ’…
রেজাউল করিম সুমন - ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯ (৬:৫৮ অপরাহ্ণ)
@ মুয়িন পার্ভেজ
১
ছন্দবিমুখ, ছন্দবিরোধী, ছন্দ-না-জানা, ছন্দ-না-মানা – এরকম নানা অভিধায় চিহ্নিত করতে পারি কাউকে, তাই বলে ‘ছন্দোমূর্খ’ হয়তো বলব না।
তিন তরুণ কবির উদ্ধৃতি থেকে বোঝা গেল, ছন্দ নিয়ে তাঁরা ভাবিত নন। একজন এমনও বলেছেন :
শেষ বাক্যটা পড়ে বিমূঢ় না হয়ে পারা যায় না।
জহর সেনমজুমদারের কবিতা আমি বেশি পড়িনি। মনে পড়ছে, সিকদার আমিনুল হকের প্রথম বইয়ে একগুচ্ছ গদ্যকবিতাও ছিল, তাঁর অন্তত দুটি বইয়ের সমস্ত কবিতাই টানাগদ্যে লেখা; কিন্তু এর বাইরেও অধিকাংশ কবিতার সাক্ষ্যে তাঁকে ছন্দবিমুখ বলার সুযোগ নেই। আব্দুল মান্নান সৈয়দ না কি একবার বলেছিলেন (বা লিখেছিলেন), অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ক্রীতদাসের মতোই সিকদারের অনুগত। কথাটা সিকদারের মুখ থেকেই শোনা।
গদ্যকবিতার সূত্রে অরুণ মিত্রের কথা মনে পড়ছে – যাঁর অধিকাংশ লেখাই টানাগদ্যে। নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, গদ্যকবিতার আঙ্গিক তিনি পেয়েছিলেন কেবল ফরাসি কবিতার ঐতিহ্য থেকে নয়, রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’ থেকেও। ছন্দোবদ্ধ আর গদ্যকবিতার মধ্য থেকে যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে, এমন শর্ত বাঙালি কবিদের সামনে সে-কালে ছিল না, এ-কালেও নেই। আবার ছন্দকে পাশ কাটিয়েও যদি কেউ কবিতা লিখতে চান, সে-পথও তো অনেককাল ধরেই খোলা। ছন্দের বিরোধিতা করতে পারেন কোনো কবি, কিন্তু কবিতাপাঠক তা পারেন না, তাঁকে স্বীকার করে নিতেই হয় কবিতার ভাষার বহুধা বৈচিত্র্যকে।
মুয়িন পার্ভেজ - ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ (১২:৫২ পূর্বাহ্ণ)
ছন্দ নিয়ে এত বেশি লেখালেখি হয়েছে যে বাঙলায়, মনে হয়, নতুন কিছুই বলার নেই আর। যুগে-যুগে প্রধান বাঙালি কবিরা নানা ছন্দের নিরীক্ষা চালিয়েছেন ব’লেই তো এত বিশ্লেষণ, ছন্দোমন্থন। কিন্তু তরুণ কবিদের কেউ-কেউ যদি ‘ছন্দ জানি না’ ব’লে আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন, তাঁদেরকে ‘ছন্দোমূর্খ’ (রূঢ় শোনালেও) ছাড়া কোন অভিধায় চিহ্নিত করা যাবে? ‘ছন্দ-না-জানা’ ও ‘ছন্দোমূর্খ’ — এই দুই অভিধার মধ্যে আছে কোনো ইতরবিশেষ?
‘ছন্দবিমুখ’ (ছন্দোবিমুখ) ও ‘ছন্দবিরোধী’ (ছন্দোবিরোধী) শব্দদু’টি ‘ছন্দোমূর্খ’-এর সমান্তরাল নয় মোটেও; আঙুরের নাগাল পাই না ব’লে আঙুর টক — এই অর্থেই কি ছন্দোবিমুখতা বা ছন্দোবিরোধিতা? যে কোনোদিন চালতা চেখে দেখেনি, সে চালতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইবে কোন যুক্তিতে? তিরিশের দশকে যাঁরা রবীন্দ্রবিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা তো সবাই রবীন্দ্রকাব্যসরোবরে অবগাহন সেরে নিয়েছিলেন আগেই। এজন্যই কবিতার ক্লাস-এ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৌতুকের ছলে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আগে অন্তত দু’-চারটি প্রচল ছন্দে কবিতা লিখে দেখাও, নইলে শুরুতেই গদ্যকবিতা লিখতে গেলে পাঠক সন্দেহ করবে!
‘গদ্যকবিতা’ বলতে গদ্যছন্দে লেখা কবিতাকেই তো বুঝি? অরুণ মিত্র রাশি-রাশি গদ্যকবিতা লিখেছেন, কিন্তু কে বলবে তাঁর কবিতাগুলো সংবাদপত্রের গদ্যভাষায় লেখা? ছন্দ মানেই অঙ্কের খেলা — সঙ্গীতের মধ্যে আছে অঙ্ক, নদীর কল্লোলের মধ্যে, এমনকী ঘোড়ার খুরের শব্দেও অঙ্ক নিহিত আছে ব’লেই মনে ভিন্ন এক দোলা তৈরি করছে। মূল কথা হল মাত্রাজ্ঞান; শুধু পদ্যছন্দেই নয়, গদ্যছন্দেও নির্মাত্র হওয়ার সুযোগ নেই কোনো। অবশ্য পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মাঝখানেও আছে অন্য এক ‘ছন্দের বারান্দা’ — ‘বৃত্তগন্ধি গদ্য’, অগ্রজ কবিরা (যেমন সৈয়দ আলী আহসানের কথাও উল্লেখ্য) তারও ক্ষমতা যাচাই ক’রে নিয়েছেন। নবীন কবিদের জন্য বহু পথ নিশ্চয়ই ‘অনেককাল ধরেই খোলা’, অর্থাৎ স্বরবৃত্তে লিখুন বা অন্য বৃত্তে আপনার যা-খুশি, কিন্তু ‘দুর্বৃত্ত’ হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা তো করতে পারেন না। আর সুনীলের কথায় ‘নিরস্ত্র হয়ে’ এলে যে পদে-পদে দুর্ঘটনা বাড়বে — এও কি অস্বীকার করা সম্ভব? ছন্দ মেনে কবিতা লেখা হয়তো কঠিন, কিন্তু ছন্দ না জেনে লেখা বিপজ্জনক।
২
বৃষ্টি ও আগুনের মিউজিকরুম নামের একটি কাব্য আছে জহর সেনমজুমদারের, এখনও পড়া হয়নি। আধুনিক বাঙলা কবিতা নিয়েও আছে তাঁর এক পরিশ্রমী গ্রন্থ (আধুনিক বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ), দেশ পত্রিকায় যার মনোজ্ঞ আলোচনা লিখেছিলেন জ্যোতিভূষণ চাকি। বোঝাই যাচ্ছে যে কবিতার সব কলাকৌশল রপ্ত ক’রেই জহর গদ্যকবিতা লিখতে এসেছেন, ‘ছন্দোমূর্খ’ (একশব্দে আর কী বলা যায়?) কবিদের নপুংসক বীরত্ব দেখাতে নয়।
৩
ছন্দ ও কবিতার টানাপোড়েন নিয়ে যা বলেছি, আমার অবস্থান স্পষ্ট করার জন্যই — কেউ ব্যক্তিগতভাবে আহতবোধ করলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। মন্তব্যের জন্য মাসুদ করিম, আসমা বীথি ও রেজাউল করিম সুমনকে অনেক ধন্যবাদ।
প্রান্ত পলাশ - ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ (১১:৩১ পূর্বাহ্ণ)
সুমন ভাইয়ের মন্তব্য পড়ে হতাশ হলাম। তিনি ‘ছন্দবিরোধী, ছন্দ-না-জানা, ছন্দ-না-মানা’ কবিদলকে ‘ছন্দোমূর্খ’ না বলে ‘ছন্দোবিমুখ’ বলার পক্ষপাতী। কিন্তু আভিধানিকভাবে ‘ছন্দ-না-জানা কবি’ ও ‘ছন্দোমূর্খ কবি’র মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না। যিনি জানেন না তিনি তো ‘মূর্খ’ই, যিনি মুখ-ই দর্শন করেননি, তাঁর বিমুখ হবার সুযোগ কোথায়? ‘ছন্দবিরোধী’ ও ‘ছন্দ-না-জানা’ শব্দবন্ধদ্বয় ছন্দোমূর্খতাপ্রকাশক নয়। অর্থাৎ তিনি ছন্দ জানেন অথচ বিরোধিতা করেন অথবা মানেন না। এখানে ‘হয়তো’ সংশয়বাচক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখি না।
আনন্দ পাচ্ছি, ছন্দ নিয়ে একটা বিতর্ক জমে উঠেছে দেখে। বর্তমানে, তথাকথিত অনেক তরুণ কবি ‘ছন্দ জানি না’ বলে বিনয় প্রকাশ করেন না, বরং ‘ছন্দ জানি না, তাই মানি না’, ‘ছন্দ প্রয়োজনীয় নয়’ ইত্যাদি-ইত্যাদি বালখিল্য-মত প্রকাশ করেন অনেকটা ঔদ্ধত্য নিয়ে। ছন্দ না জেনে অনেকেই তাকে ‘কাঠামোগত সূত্র’ বলে এড়িয়ে যেতে চান, আর ‘গদ্যকবিতার’ ঢোল পেটান। কিন্তু গদ্যকবিতাই বা কী, তাঁরা জানেন কি না আদৌ, সন্দেহ জাগে!
কবিতার ছন্দ দুই প্রকারের : পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ। একটি ‘বাঁধা’, অপরটি ‘অ-বাঁধা’। অর্থাৎ পদ্যছন্দ গদ্যছন্দের মতো অতটা মুক্ত নয় — সাধারণত এ-সবই প্রচলিত মত। কিন্তু মহৎ কবিদের হাতে এসব ‘বাঁধা’র বন্ধন অনেকটাই খুলে গেছে। যিনি ছন্দ জানেন, তিনি তা নিয়ে খেলতেও জানেন। আর যিনি জানেন না, তাঁর কথা তো ধর্তব্যই নয়!
কবিতার প্রয়োজনেই ছন্দ — তা, যতটা না আঙ্গিকের, তার চেয়ে বেশি ভাবের। কোনো কথা দ্বারা শুধুই অর্থ প্রকাশ পায়, তা চিত্তকে দোলা দিতে পারে না। এই দোলা বা নাড়া দেবার জন্য প্রয়োজন বেগ বা গতি, যা ঐ কথাকেই ‘পরম অর্থে’র দিকে ধাবিত করে। সেই আলোড়ন ব্যাখ্যাতীতও হতে পারে, কিন্তু তা চিত্তস্পর্শী। এই বেগ বা গতির নামই ছন্দ। কবি বাক্যের ভেতর পদ বা পর্ববিভাজনের মাধ্যমে এই গতিকে থামাতে বা বাড়াতে পারেন। এ যেন ঢেউ। কিন্তু কবিকে সতর্ক থাকতে হয় বাক্যের চলনের দিকে। এভাবে, ‘চাল’ ও ‘চলন’ _ দুইয়ের ভারসাম্যেই ছন্দ। পদ্য ও গদ্য, উভয় ছন্দই এই ভারসাম্য দাবি করে, না হলে ‘চালচলনহীন’ বদ্ধ-উন্মাদের মতো শব্দসমুদয় খিলখিল করে হাসে! তাই কোনো কবিতায় ‘বিশ্ববোধের ইশারা’, ‘প্রশ্ন তুলতে পারার’ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা ‘ভালো কবিতা’ হয়ে উঠতে পারে না। কবিতায় ছন্দই যদি না থাকল, তাহলে তা অন্যান্য রচনা বা প্রবন্ধ থেকে পৃথক কেন? সে-কারণে ‘গদ্যকবিতা’ মানেই ‘গদ্যছন্দে লিখিত কবিতা’, এছাড়া ‘গদ্যকবিতা’ নামে আলাদা কিছু নেই। তাই কবি চাইলেই ‘ছন্দকে পাশ কাটিয়ে যেতে’ পারেন না!
যে-কবি ছন্দই জানেন না, তিনি ঐ ‘দোলা’ টের পাবেন কী করে? যাঁর ‘মর্ম’ ‘স্পর্শে’র জন্য প্রস্তুত নয়, তিনি কীভাবে বুঝবেন কোনটা ‘মর্মস্পর্শী’? তাই ‘ছন্দবিরোধী, ছন্দ-না-জানা, ছন্দ-না-মানা’ কবিদলকে সামগ্রিক অর্থে ‘ছন্দোমূর্খ’ বলার পক্ষপাতী আমি।
আমি জানি, সুমন ভাই শুধু ছন্দ নয়, অন্যান্য অনেক বিষয়েই সুজ্ঞানী এবং কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হলে তিনি মন্তব্য করেন না। তাঁর কাছ থেকে ‘হয়তো’ সংশয়বাচক শব্দ আমি কি আশা করতে পারি?
মাসুদ করিম - ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ (১০:৫৭ অপরাহ্ণ)
সেই তো অমলিন হাওয়া
ছন্দের স্বাধীনতা
আমি চাই
আর তুমি
রেজাউল করিম সুমন - ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ (৮:১৮ অপরাহ্ণ)
@ মুয়িন পার্ভেজ, প্রান্ত পলাশ
ধন্যবাদ সংগত প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য।
আগের মন্তব্যে লিখেছিলাম,
বলা বাহুল্য, এ অবস্থান একান্তই আমার। আমাকে কেউ ছন্দোমূর্খ বললে আপত্তি করব না; কিন্তু আমি কাউকে সে-অভিধা দেব না। অন্যকে ‘– মূর্খ’ বলতে পারি কেবল নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার পরই, তার আগে নয়। আর তাছাড়া, মূর্খের সঙ্গে তর্ক চলে না, সংলাপও না। আমি সুযোগ থাকলে সংলাপে আগ্রহী।
মাসুদ করিম - ২৪ আগস্ট ২০০৯ (২:৫৫ অপরাহ্ণ)
আমরা তিনটি প্রক্রিয়ার কোনোটিকেই হারাতে চাই না বা কটাক্ষ করতে চাই না। নানা ছন্দে লেখা কবিতা, ছন্দ জেনে ব্যবহার করা না করা কবিতা, ছন্দ না জেনে লেখা কবিতা। আমরা কবিতাকেই ধরতে চাই। বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছিলেন : তুমি এসো, তুমি এসো, তুমিও এসো।
আসমা বীথি - ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ (১:৫৬ পূর্বাহ্ণ)
উত্তীর্ণ কবিতার যে অবয়বটি পেলাম মুয়িনের ব্যখ্যায় তার সাথে ৩.১.১.১-এর চিন্তার বিরোধ কোথায় বোঝা গেল না। বিরোধ, ছন্দ নিয়েই বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু লেখাটিতে ছন্দ শব্দটির উল্লেখ বার কয়েক থাকলেও মূল বিষয় তো তা ছিল না; বা ছন্দকে অগ্রাহ্যও করা হয়নি কোথাও। ভালো লেখার যে সংজ্ঞাটি শঙ্খ দিয়েছেন সেখানে ’নতুন চোখে দেখতে পাবার ক্ষমতার’-ও উল্লেখ ছিল। সেই দেখার সত্যতার দারুণ উদাহরণ টেনে দেখিয়েছেন শামসুরের ‘কাল সারারাত’ কবিতার মধ্য দিয়ে মুয়িন নিজেই।
এই যে অভিমুখীনতা, আলোড়ন, দ্বান্দ্বিক চেতনার অভিজ্ঞতা থেকে তৃতীয় কোনও স্বরের উন্মোচন — আজ অনেক বেশি দরকার।
সম্ভবত মন্তব্যের ঘরে আমার ছোট্ট আলোচনা এই বোধগুলোকেই জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল, শঙ্খের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে। অর তথাকথিত তরুণ কবিদের ছন্দোমূর্খতা ওই আলোচনায় টেনে আনাকে মনে করেছিল অপ্রাসঙ্গিক, অযাচিত। কেননা ছন্দের ট্রেন বহু আগেই ছেড়ে গেছে প্লাটফর্ম!
মুয়িন পার্ভেজের এই আলোচনা আরো বিস্তারিত হয়ে আলাদা একটি পোস্ট দাবি করছে।
ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজ।
মাসুদ করিম - ২৬ জানুয়ারি ২০১১ (৯:২৩ পূর্বাহ্ণ)
পদ্মভূষণ সম্মান পেলেন শঙ্খ ঘোষ। খবরের লিন্ক এখানে।
মাসুদ করিম - ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ (১১:৪২ পূর্বাহ্ণ)
রেজাউল করিম সুমন - ১০ জানুয়ারি ২০১৭ (৮:২২ অপরাহ্ণ)
সংবাদ প্রতিদিন-এর রোববার-এ প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কিত কয়েকটি লেখা পড়া যাবে এই লিংকে ক্লিক করে।
মাসুদ করিম - ২১ এপ্রিল ২০২১ (১০:৩৯ পূর্বাহ্ণ)
কবিতার মুহূর্ত স্তব্ধ, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কেড়ে নিয়ে গেল কবি শঙ্খ ঘোষকে
প্রয়াত শঙ্খ ঘোষ। শক্তি-সুনীল-শঙ্খ-উৎপল-বিনয়, জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতার এই পঞ্চপাণ্ডবের বাকি চার জন চলে গিয়েছিলেন আগেই। চলে গেলেন শঙ্খবাবুও। ৮৯ বছর বয়সে। বুধবার নিমতলা মহাশ্মশানে রাষ্ট্রীয় সম্মানে শেষকৃত্য হবে তাঁর। তবে বরাবর তোপধ্বনিতে আপত্তি ছিল কবির। তাই তোপধ্বনি বাদ রেখেই শেষকৃত্য হবে।
গায়ে জ্বর থাকায়, গত সপ্তাহে করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন কবি। ১৪ এপ্রিল বিকেলে রিপোর্ট এলে জানা যায়, তিনি সংক্রমিত হয়েছেন। এমনিতেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন কবি, যা শারীরিক ভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল তাঁকে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে এ বছর জানুয়ারি মাসে হাসপাতালেও ভর্তি করতে হয় তাঁকে।
তাই কোভিড সংক্রমণ ধরা পরার পর ঝুঁকি না নিয়ে বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন। তিনি নিজেও হাসপাতালে যেতে চাননি। তাই বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল।কিন্তু মঙ্গলবার রাতে আচমকাই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। বুধবার সকালে তাঁকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চলে গেলেন কবি। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ভেন্টিলেটর খুলে নেওয়া হয়।
কবির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘শঙ্খদার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করছি। তাঁর পরিবার এবং শুভানুধ্যায়ীদের সকলকে সমবেদনা জানাই। কোভিডে মারা গিয়েছেন শঙ্খদা। তা সত্ত্বেও যাতে রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা যায়, মুখ্যসচিবকে তেমন নির্দেশ দিয়েছি। তবে শঙ্খদা গান স্যালুট পছন্দ করতেন না। সেটা বাদ রাখছি।’’
দীর্ঘ কর্মজীবনে নানা ভূমিকায় দেখা গিয়েছে শঙ্খবাবুকে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনাও করেছেন। ইউনিভার্সিটি অব আইওয়ায় ‘রাইটার্স ওয়ার্কশপ’-এও শামিল হন। বছর দুয়েক আগে ‘মাটি’ নামের একটি কবিতায় কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছিলেন তিনি।
বাংলা কবিতার জগতে শঙ্খ ঘোষের অবদান কিংবদন্তিপ্রতিম। ‘দিনগুলি রাতগুলি’, ‘বাবরের প্রার্থনা’, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’, ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তাঁর প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত।
দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। ১৯৭৭ সালে ‘বাবরের প্রার্থনা’ কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ১৯৯৯ সালে কন্নড় ভাষা থেকে বাংলায় ‘রক্তকল্যাণ’ নাটকটি অনুবাদ করেও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান তিনি। এ ছাড়াও রবীন্দ্র পুরস্কার, সরস্বতী সম্মান, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১১ সালে তাঁকে পদ্মভূষণে সম্মানিত করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার।
https://twitter.com/MyAnandaBazar/status/1384759438012084227